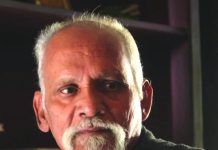ইনফোডেমিক: একটি বৈশ্বিক সংকট
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রথমবারের মতো কোভিড–১৯ মহামারির সময় ‘ইনফোডেমিক’ শব্দটি ব্যবহার করে। এটি বোঝায়, ভুয়া তথ্য এবং গুজবের অতিরিক্ত প্রবাহ যা মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এই বৈশ্বিক সমস্যা বিশেষত ভারতের মতো দেশগুলিতে বড় আকারে প্রভাব ফেলেছে, যেখানে বিশাল জনসংখ্যা এবং ডিজিটাল মিডিয়ার ব্যাপক ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও এই সমস্যার প্রভাব লক্ষ্যণীয়।
ভারত: ভুয়া তথ্যের কেন্দ্রবিন্দু
মাইক্রোসফটের সামপ্রতিক এক জরিপে প্রকাশিত হয়েছে যে, ৬৪% ভারতীয় ভুয়া তথ্যের সম্মুখীন হয়েছেন, যা বৈশ্বিক গড় ৫৭% এর চেয়ে অনেক বেশি। জরিপে আরও দেখা যায় যে, ২৯% অনলাইন ঝুঁকি আসে পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের কাছ থেকে। এটি প্রমাণ করে, ভুয়া তথ্য কেবল গণমাধ্যমের মাধ্যমেই নয়, ব্যক্তিগত সংযোগের মাধ্যমেও ছড়ায়।
ভারতীয় গণমাধ্যমে ইনফোডেমিকের প্রভাব:
ভারতে গুজব ছড়ানোর সবচেয়ে বড় মাধ্যম হয়ে উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়া। একদিকে গণমাধ্যমের একাংশ দ্রুত খবর প্রচারের চাপে যাচাই ছাড়াই তথ্য প্রকাশ করছে; অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে অপপ্রচার নিয়ন্ত্রণ করার যথেষ্ট ব্যবস্থা নেই। উদাহরণস্বরূপ, ঈঙঠওউ–১৯ মহামারির সময়, ভ্যাকসিন নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য এবং গুজব দেশের স্বাস্থ্য খাতকে একটি বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে।
বাংলাদেশের সাথে তুলনামূলক প্রেক্ষাপট:
বাংলাদেশেও ইনফোডেমিকের প্রভাব কম নয়। উদাহরণস্বরূপ, পদ্মা সেতু নির্মাণের সময় ‘মানববলির’ গুজব সারা দেশে আলোড়ন তোলে। এটি মানুষের আস্থা কমিয়ে দেয় এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। ভারতের মতো বাংলাদেশেও গণমাধ্যমের একটি অংশ যাচাই–বাছাই ছাড়াই তথ্য প্রকাশ করে এবং কিছু সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী ভুয়া তথ্য ছড়ানোর হাতিয়ারে পরিণত হয়।
ইনফোডেমিক নিয়ন্ত্রণে সম্ভাব্য পদক্ষেপ:
ভারত এবং বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা থেকে শিখে, ইনফোডেমিক মোকাবিলায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে:
১. তথ্য যাচাই এবং ফ্যাক্ট–চেকিং: ভুয়া তথ্য প্রতিরোধে মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্রিয় ভূমিকা অপরিহার্য।
২. মিডিয়া সাক্ষরতা বৃদ্ধি: স্কুল এবং কলেজ পর্যায়ে মিডিয়া সাক্ষরতার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।
৩. আইন প্রয়োগ: সাইবার ক্রাইম ইউনিটগুলোকে আরও সক্রিয় করতে হবে।
৪. প্রযুক্তি ব্যবহার: ফেক নিউজ শনাক্ত করার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক টুল আরও উন্নত করতে হবে।
ভারতীয় গণমাধ্যম থেকে একটি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টিভঙ্গি:
ভারতীয় মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ার ইনফোডেমিক থেকে শেখার বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, মিডিয়া নীতি এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উভয় দেশই এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে নিতে পারে। ভারতের টিভি চ্যানেলগুলো এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো বিশ্বে তাদের বিশাল দর্শক সংখ্যা এবং প্রভাবের জন্য সুপরিচিত। তবে সামপ্রতিক বছরগুলোতে এই মাধ্যমগুলোর একটি বড় অংশ ভুয়া তথ্য ছড়ানোর প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে। দ্রুত সংবাদ প্রচারের প্রতিযোগিতা এবং নাটকীয় উপস্থাপনার কারণে সত্যের চেয়ে সংবেদনশীলতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।
টিভি চ্যানেল ও ভুয়া সংবাদ প্রচার
ভারতীয় টিভি চ্যানেলগুলোর একটি বড় অংশ বিশেষত নেতিবাচক এবং ভুল তথ্য প্রচারের জন্য পরিচিত। তারা প্রায়ই চমকপ্রদ হেডলাইন তৈরি করে এবং প্রমাণ ছাড়াই তথ্য প্রচার করে। উদাহরণস্বরূপ:
১. সীমান্ত পরিস্থিতি: ভারতীয় টিভি চ্যানেলগুলো প্রায়ই প্রতিবেশী দেশগুলোর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন খবর প্রচার করে। এই ধরনের খবর শুধু জাতীয়তাবাদকে উস্কে দেয় না, বরং পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটায়।
২. ধর্মীয় বিভাজন: ভারতে সামপ্রদায়িক উত্তেজনা বাড়ানোর ক্ষেত্রে টিভি চ্যানেলগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। সংখ্যালঘু সমপ্রদায়ের বিরুদ্ধে অপপ্রচার এবং অতিরঞ্জিত রিপোর্টিং প্রায়ই সহিংসতা উস্কে দেয়।
৩. রাজনৈতিক প্রভাব: রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাব ভারতীয় টিভি চ্যানেলগুলোকে নিরপেক্ষতার পরিবর্তে পক্ষপাতদুষ্ট রিপোর্টিংয়ে বাধ্য করে।
সোশ্যাল মিডিয়া: একটি বিভ্রান্তির প্ল্যাটফর্ম:
সোশ্যাল মিডিয়া ভারতীয় সমাজে তথ্যের দ্রুত বিস্তারের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। তবে এটি ভুয়া তথ্যের জন্য একটি উর্বর জমি হিসেবেও পরিচিত হয়ে উঠেছে।
১. বিতর্কিত পোস্ট এবং ভিডিও: অনেক জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট প্রায়ই ভুয়া ভিডিও এবং বিকৃত তথ্য ছড়ায়। উদাহরণস্বরূপ, কৃষক আন্দোলনের সময় অনেক ভুয়া ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল, যা পরিস্থিতি আরও জটিল করে তোলে।
২. অপপ্রচার চালানোর জন্য বট অ্যাকাউন্ট: সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে বট অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে ভুয়া তথ্য এবং গুজব ছড়ানো একটি সাধারণ কৌশল হয়ে উঠেছে।
৩. হ্যাশট্যাগ ম্যানিপুলেশন: ভুল তথ্য ছড়ানোর জন্য প্রায়ই হ্যাশট্যাগ ম্যানিপুলেশন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ইস্যুতে মনোযোগ ঘোরানোর জন্য ভিন্নধর্মী হ্যাশট্যাগ ট্রেন্ড করানো হয়।
ইনফোডেমিকের নেতিবাচক প্রভাব: ভারতীয় গণমাধ্যম থেকে শিক্ষা
ভারতীয় টিভি ও সোশ্যাল মিডিয়ার ভুয়া তথ্য ছড়ানোর ঘটনা শুধুমাত্র স্থানীয় সমাজে নয়, আন্তর্জাতিকভাবে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশের জন্য এটি একটি সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করতে পারে।
১. সামাজিক বিভক্তি: ভুয়া তথ্য এবং অপপ্রচারের কারণে সমাজে বিভাজন এবং উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।
২. অর্থনৈতিক সংকট: ভুয়া তথ্যের কারণে বিনিয়োগকারীদের আস্থা কমে যায়, যা অর্থনৈতিক অস্থিরতার কারণ হতে পারে।
৩. গণতন্ত্রের হুমকি: মিডিয়া যখন পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পডড়ে, তখন তা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর মানুষের আস্থা নষ্ট করে।
ইনফোডেমিক নিয়ন্ত্রণে সম্ভাব্য কৌশল
ভারতীয় মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে শেখার মাধ্যমে বাংলাদেশসহ অন্য দেশগুলো তাদের নিজস্ব গণমাধ্যমে ভুয়া তথ্য প্রতিরোধের জন্য কৌশল গ্রহণ করতে পারে।
১. ফ্যাক্ট–চেকিং প্ল্যাটফর্মের প্রসার: তথ্য যাচাই করার জন্য আরো প্ল্যাটফর্ম চালু করতে হবে।
২. মিডিয়া নীতিমালা শক্তিশালী করা: মিডিয়ার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা প্রয়োজন, যা সাংবাদিকতার মান বজায় রাখতে সহায়ক হবে।
৩. জনসচেতনতা বৃদ্ধি: সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের শিক্ষিত করা এবং ভুয়া তথ্য শনাক্ত করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।
ভারতীয় টিভি চ্যানেল এবং সোশ্যাল মিডিয়া যেভাবে ইনফোডেমিক ছড়াচ্ছে, তা শুধু তাদের দেশের জন্য নয়, প্রতিবেশী দেশগুলোর জন্যও একটি বড় হুমকি। তবে এই পরিস্থিতি আমাদের শেখার সুযোগও তৈরি করে। তথ্যের শক্তি দ্বিমুখী, এবং এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার দায়িত্ব গণমাধ্যম, সরকার, এবং নাগরিক সবার। বাংলাদেশের মতো দেশগুলো ভারতীয় মিডিয়ার ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে একটি সুরক্ষিত তথ্য পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে।
লেখক: সিনিয়র ম্যানেজার, স্ট্র্যাটেজিক সেলস, এলিট পেইন্ট এন্ড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রীজ লিঃ