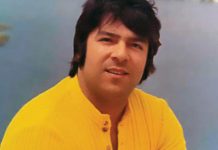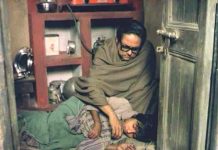আকাশে যখন ভোরের আলো ফোটে, পুরান ঢাকার কুমারটুলি এলাকায় বুড়িগঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে থাকা এক বিশাল প্রাসাদ যেন ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে নতুন দিনের সূচনা করে। প্রাসাদটি আহসান মঞ্জিল, যা ‘পিংক প্যালেস’ বা ‘গোলাপি প্রাসাদ’ নামে পরিচিত। একসময় এটি ছিল নবাব পরিবারের বাসভবন ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র। আজ তা রূপান্তরিত হয়েছে জাদুঘরে। তবে আহসান মঞ্জিলের গুরুত্ব কেবল রাজকীয় আভিজাত্য বা স্থাপত্যকীর্তিতে সীমাবদ্ধ নয়; এটি আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাজীবনের ইতিহাসের সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম–সবকিছুরই সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই প্রাসাদের নাম।
আহসান মঞ্জিল–বাংলার নবাব পরিবারের আভিজাত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি এবং জীবনের উত্থানপতনের অমূল্য প্রতিচ্ছবি। প্রাসাদে প্রবেশের সুবিশাল সিঁড়ি যেন ইতিহাসের দরজা যা সবার জন্য উন্মুক্ত। আহসান মঞ্জিলে প্রবেশ করলে মনে হয়, সময় এখানে থমকে গেছে। প্রতিটি ঘর, প্রতিটি সিঁড়ি, প্রতিটি জানালা অতীতের গল্প বলে চলে। এখানে যেমন গৌরবের ইতিহাস আছে, তেমনি আছে নিস্তব্ধ বেদনার স্মৃতি ।
উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, ১৭২০ এ বর্তমান আহসান মঞ্জিল এলাকায় মোগল জমিদার শেখ ইনায়েতউল্লাহর বাগানবাড়ি ছিল, যা ১৭৪০ সালে ফরাসি বণিকগণ শেখ ইনায়েতউল্লাহর পুত্র শেখ মতিউল্লাহ্র কাছ থেকে নিয়ে বাণিজ্যকুঠি তৈরি করে। ১৮৩০ সালে খাজা আলীমুল্লাহ ফরাসিদের নিকট হতে কুঠিবাড়িটি ক্রয় করে সংস্কারের মাধ্যমে বাসভবনোপযোগী করেন। ১৮৫৯ সালে নওয়াব আবদুল গনি ফরাসি কুঠিরের পূর্ব পার্শ্বে নতুন প্রাসাদ নির্মাণ শুরু করেন, যা ১৮৭২ সালে শেষ হয় এবং তিনি তাঁর পুত্র খাজা আ্হসানউল্লাহর নামে নামকরণ করেন আহসান মঞ্জিল।
আকারে বিশাল এই প্রাসাদের স্থাপত্যশৈলী মোগল ও ইউরোপীয় ধাঁচের মিশ্রণ। বিশাল গম্বুজ, দৃষ্টিনন্দন খিলান, প্রশস্ত সিঁড়ি এবং বারান্দা একে রাজকীয় সৌন্দর্যে ভরিয়ে তুলেছে। ব্রিটিশ ঔপনেবেশিক শাসনের সময় বহু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং বিদেশি অতিথি এই প্রাসাদের আতিথেয়তা গ্রহণ করেছেন।
ভবনটি দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত–রঙমহল ও অন্দর মহল। নবাবদের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড, অতিথি সংবর্ধনা, সাংস্কৃতিক আসর, সামাজিক ও রাজনৈতিক আয়োজন–সবই
রংমহলকে ঘিরে আবর্তিত হতো। অন্যদিকে, অন্দরমহল ছিল পরিবারের বসবাসের স্থান। পৃথক দুটি ভবনে যাতায়াতের জন্য দ্বিতীয় তলায় ছিলো সংযোগ সেতু যা পদচারী সেতু বলে পরিচিত।
বর্তমানে এই দুটি মহলই জাদুঘর হিসেবে সংরক্ষিত আছে। বিভিন্ন কক্ষে সাজানো আছে নবাব পরিবারের ব্যবহৃত অলঙ্কার, পোশাক, নানাবিধ শিল্পকর্ম, তৈজসপত্র ও নবাবের প্রহরীদের অস্ত্রশস্ত্র। জাদুঘরে সর্বমোট ৪০৭৭ টি নিদর্শন প্রদর্শন করা হয়। আহসান মঞ্জিলের জন্য নিদর্শনসমূহ সাধারণত দুই উপায়ে সংগ্রহ করা হয়। প্রথমত, নওয়াব এস্টেটের পুরোনো অফিস এডওয়ার্ড হাউজ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন নিদর্শন এবং অন্য একটি হল–লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে প্রাপ্ত ও মি. ফ্রিটজকাপ কর্তৃক ১৯০৪ সালে তোলা আলোকচিত্রের সাথে মিলিয়ে বিভিন্ন আসবাবপত্র ও সমসাময়িক নিদর্শনাদি সংগ্রহ করে প্রদর্শনীর জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।
ঢাকার নবাব পরিবার ছিলো ব্রিটিশ বাংলার সবচেয়ে বড় মুসলিম জমিদার পরিবার। সিপাহী বিপ্লবের সময় ব্রিটিশদের প্রতি বিশ্বস্ততার জন্য ব্রিটিশ রাজ এই পরিবারকে নবাব উপাধিতে ভূষিত করে। পরিবারটি স্বাধীন না হলেও দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে নবাব পরিবারের ভূমিকা ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা ঢাকা শহরকে আধুনিক নগরীতে রূপ দিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি ও অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করেন। ঢাকার প্রথম বিদ্যুৎ ব্যবস্থা চালু করেছিলেন নবাব আহসানউল্লাহ।
নবাব সলিমল্লাহ মুসলিম শিক্ষার প্রসার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। তিনি একজন প্রজা অন্তঃপ্রাণ দয়ালু নবাব হিসেবে সুপরিচিত যার দানে বদলে গিয়েছিলো ঢাকার ইতিহাস।
বৃটিশ শাসনের অবসানে জমিদারী প্রথা বিলুপ্তির পর নবাব পরিবারের জৌলুস ধীরে ধীরে কমে যায়। আয়ের মূল উৎসও বন্ধ হয়ে যায়। নবাব পরিবারের সদস্যদের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্য কমতে থাকে। নবাবের উত্তরাধিকারীদের পক্ষে বিশাল প্রাসাদের ব্যয় নির্বাহ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। শেষ জমিদার খাজা হাবিবুল্লাহ প্রাসাদ ছেড়ে পরীবাগ গ্রিন হাউসে বসবাস শুরু করেন। অংশীদারগণ বাছবিচার না করে প্রাসাদের কক্ষসমূহ ভাড়া দেওয়ায় ভবনটি ধ্বংসের দিকে যেতে থাকে।
অবশেষে পাকিস্তান আমলে সরকার এটি অধিগ্রহণ করে এবং পরবর্র্তীতে বাংলাদেশ সরকার এর পুনঃনির্মান ও সংস্কার করে জাদুঘরে রূপান্তরিত করে। ১৯৯২ সাল হতে জাদুঘরটি সর্বসাধারণের প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া হয়। এভাবেই যে প্রাসাদে একসময় নবাব পরিবারের রাজত্ব ছিলো, আজ তা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত।
আহসান মঞ্জিল কেবল একটি প্রাসাদ নয়, এটি বাংলার ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি। এখানে আভিজাত্যের গৌরব যেমন আছে, তেমনি পতনের বেদনাও আছে। প্রাসাদের প্রতিটি ইট, প্রতিটি আসবাব, দেয়ালে ঝুলানো অসংখ্য ছবি আমাদের বলে যায়–মানুষ চলে যায়, থেকে যায় শুধু তার গল্প। বিস্মৃত অতীতে হারিয়ে যান এক সময়ের দাপুটে ক্ষমতাবানরা। রেখে যান কেবল ইতিহাসের প্রতিধ্বনি আর শূন্য প্রাসাদের স্মৃতি। পুরান ঢাকার বেগমবাজার এলাকায় পারিবারিক কবরস্থানে চিরশায়িত আছেন নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, নবাব আহসানউল্লাহ এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ।
আহসান মঞ্জিল ভ্রমণ শেষে আমি যেমন বিস্মিত হয়েছি, তেমনি বেদনাবোধেও আচ্ছন্ন হয়েছি। প্রশস্ত বারান্দা থেকে বুড়িগঙ্গার সৌন্দর্য উপভোগ করার কল্পনা কিংবা দীর্ঘ ডাইনিং টেবিলে পারিবারিক ভোজের দৃশ্য আমার মনে অতীতের আবহকে জাগিয়ে তুলেছিল। একসময় যে বারান্দা ছিল পরিবারের সদস্যদের আনন্দময় মুহূর্তের সঙ্গী, আজ তা পর্যটকদের ভীড়ে মুখর। যে টেবিলে সবাই মিলে আহার করতেন, আজ তা নিছক প্রদর্শনীর জিনিস। ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, হাসি–আনন্দ আর পারিবারিক বন্ধন–সবই আজ ইতিহাসে বন্দী।
আহসান মঞ্জিল আমাদের উপলব্ধি করায়–জীবন ক্ষণস্থায়ী। রাজত্ব, আভিজাত্য, সম্পদ–সবকিছুই একসময় বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু ইতিহাসে থেকে যায় কেবল মানুষের কর্ম ও তার স্মৃতি।