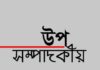দারিদ্র্য শব্দটি অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের আর্থিক ক্রয়ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে দারিদ্র্য শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। তবে এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদরা একমত নয়। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে দরিদ্র বলা হবে তা নিয়ে ব্যাপক মতভেদ আছে। প্রাথমিকভাবে দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছিল মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে। এতে ব্যাপক অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাথাপিছু আয় কম। কিন্তুু এসব জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত পণ্যের দামও কম। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, একটি দরিদ্র দেশের একজন ক্রেতা একটি ভাল মানের শার্ট যদি ক্রয় করতে চায় তবে তাকে এক হাজার থেকে দুই হাজার টাকার মত পরিশোধ করতে হয়। যদি আন্তর্জাতিক ডলারে (আমেরিকান ডলার) রূপান্তর করি তবে বলা যায়, ক্রেতাকে ১০ ডলার থেকে ১৮ ডলার (এক ডলার = ১২০ টাকা) পরিশোধ করতে হয়। অথচ সমগ্র ইউরোপে এরূপ মানের একটি শার্ট ক্রয় করার জন্য ৫০ থেকে ১০০ ডলার ব্যয় করতে হয়। একইভাবে বলা যায়, সমগ্র ইউরোপে এক কাপ কফির জন্য ব্যয় করতে হয় প্রায় এক থেকে দুই ডলার, যা বাংলাদেশের টাকায় একশত বিশ টাকা থেকে দুইশত চল্লিশ টাকা। অথচ একজন সাধারণ ক্রেতা বাংলাদেশে এক কাপ কফির জন্য ব্যয় করে সর্বাধিক পঞ্চাশ টাকা থেকে ষাট টাকা। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পাঁচ তারকা হোটেলগুলোকে উহ্য রাখা হয়েছে। কারণ সাধারণ মানুষ বা ক্রেতা এসব হোটেলে সাধারণত যায় না। কাজেই পণ্যের দামের পার্থক্য থাকার কারণে মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে দারিদ্র্যের সংজ্ঞাটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে গ্রহণযোগ্য হয় না। ফলে অর্থনীতিবিদরা দারিদ্র্যের সংজ্ঞাকে পরিবর্তন করে বললেন, পুষ্টি গ্রহণের ভিত্তিতে দারিদ্র্যের সংজ্ঞা হওয়া উচিত। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী দারিদ্র্য হচ্ছে খাদ্য গ্রহণের এমন একটি স্তর যা থেকে প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চয়ের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ কিলো–ক্যালরি পাওয়া যায় না। দারিদ্র্র্যপীড়িত জনসংখ্যার প্রাক্কলন কয়েকটি পদ্ধতিতে প্রস্তুুত করা হয়। ভোগ অভ্যাস এবং ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় করে একটি খাদ্য তালিকা চিহ্নিত করা হয়। এ তালিকা অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিদিন ২১১২ কিলো–ক্যালরি এবং ৫৮ গ্রাম প্রোটিন গ্রহণ করতে হয়। এর কম কিলো–ক্যালরি ও প্রোটিন গ্রহণ করলে তারাই দরিদ্র।
দারিদ্র্যের এ সংজ্ঞাতেও অনেক অর্থনীতিবিদ একমত হতে পারেনি। তারা আর একটি নিয়মে দারিদ্র্য পরিমাপ করতে উদ্যোগী হন। ব্যাপক ও বিস্তারিত গবেষণা করে একটি দারিদ্র্য রেখা উদ্ভাবন করেন। এ দারিদ্র্য রেখার নীচে যাদের অবস্থান তারা দরিদ্র। এ ক্ষেত্রে দারিদ্র্যকে তারা কয়েক ভাগে ভাগ করেন। যেমন চরম দারিদ্র্য ও আপেক্ষিক দারিদ্র্য। চরম দারিদ্র্য হলো মৌলিক চাহিদা যেমন– অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান পূরণে অক্ষমতা, যা সর্বজনীন ও অপরিবর্তনীয়। অন্যদিকে আপেক্ষিক দারিদ্র্য হলো সমাজে অন্যদের তুলনায় জীবনযাত্রার নিম্নমান, যা স্থান ও কালের প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন হয়। চরম দারিদ্র্যকে সরাসরি মৌলিক চাহিদার অভাব দিয়ে পরিমাপ করা হয়, যেখানে আপেক্ষিক দারিদ্র্যকে পরস্পর তুলনা ও বণ্টনের মাধ্যমে মাপা হয়। প্রতি বছর ১৭ অক্টোবর আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবস হিসেবে সারা বিশ্বে পালিত হয়। এ দিবসটি এমন এক সময় পালিত হচ্ছে, যখন বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ দারিদ্র্যের হার বাংলাদেশে বৃদ্ধির কথা বলেছে দেশি ও বিদেশি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্বব্যাংক। দারিদ্র্য বিমোচনের সাফল্যের জন্য ২০১৬ সালে বাংলাদেশে কর্মসূচী পালন করেছিল বিশ্বব্যাংক। বিশ্বব্যাংকের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম ঢাকায় এসে ‘দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্বে বাংলাদেশ’ শীর্ষক গণবক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিন্তুু এখন দারিদ্র্য বিমোচন উল্টো পথে হাঁটছে বাংলাদেশ। অতি সম্প্রতি বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান– ‘পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার’– (পিপিআরসি) এর ‘ইকোনমিক ডায়নামিকস অ্যান্ড মুড অ্যার্ট হাউসহোল্ড লেবেল ইন মিড ২০২৫’– শীর্ষক গবেষণার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে এখন দারিদ্র্যের হার ২৭ দশমিক ৯৩ বা প্রায় ২৮ শতাংশ। তাছাড়া এই গবেষণায় আরো দেখা যায়, বাংলাদেশে আরো ১৮ শতাংশ মানুষ যে কোনো সময় গরীব হওয়ায় ঝুঁকিতে রয়েছে। তাছাড়া ‘বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো’– (বিবিএস) ২০২২ সালের জাতীয় খানা আয় ও ব্যয় জরিপ অনুসারে ঐ বছর দারিদ্র্যের হার ছিল ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ। এরপর বিবিএস এ সম্পর্কিত বাংলাদেশের জরিপ করেনি। ২০২২ সাল থেকে ২০২৫ সালে বাংলাদেশের জরিপে দেখা যায়, মাত্র তিন বছরে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ থেকে ২৭ দশমিক ৯৩ শতাংশ বা প্রায় ২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ ২০২২ সাল থেকে ২০২৫ সালে মাত্র তিন বছরে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার প্রায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মানে হলো দারিদ্র্য লোকের সংখ্যা বেড়েছে প্রতি ১০০ জনে ১০ জন। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রতি ৪ জনে ১ জন দরিদ্র। অথচ ২০২৬ সালে বিবিএস জরিপের তথ্য অনুসারে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল প্রায় ২৪ শতাংশ। যদি ২০১৬ সালের পরবর্তী ২০২২, ২০২৪ এবং ২০২৫ সালে বাংলাদেশের দারিদ্র্য হারের মধ্যে তুলনা করা হয় তবে দেখা যায় ২০২২ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ (বিবিএস জরিপ)। ২০২৪ সালে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পরিমাপকৃত বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ২১ দশমিক ২ শতাংশ। আর ২০২৫ সালে পিপিআরসি কর্তৃক পরিমাপকৃত বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার হয় ২৭ দশমিক ৯ শতাংশ। কিন্তুু দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধির কারণ কী? বিশ্বব্যাংক পিপিআরসি, সানেম সহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দারিদ্র্যের হার বেড়েছে। যদিও প্রতিটি গবেষণার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। বিভিন্ন জরিপের মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা গেলেও বাংলাদেশে দারিদ্র্য বৃদ্ধি নিয়ে সব প্রতিষ্ঠান একমত। ছোটখাটো দুর্যোগ হলে বিপুলসংখ্যক মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে নেমে যায়। বাংলাদেশে এখন অন্তত ১০ কোটি মানুষ দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে রয়েছে। এরূপ দারিদ্র্য বৃদ্ধির তিনটি কারণ রয়েছে বলা যায়। প্রথমত: ২০২২ সালের পরবর্তী সময়ে সকল প্রকার ব্যবহার্য পণ্যের দাম যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে সেই হারে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়নি। ফলে ভোক্তার জীবনযাত্রার মান নিচে নেমে গেছে। আর ভোক্তা ক্রমাগত দরিদ্র হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ২০২৬ সালের পরবর্তী শিল্পখাতে কর্মসংস্থানের পরিমাণ আনুপাতিক হারে বাড়েনি। অর্থাৎ চাহিদা অনুসারে কর্মসংস্থান হয়নি। যে পরিমাণ জনসংখ্যা কর্মসংস্থানের বাজারে প্রবেশ করেছে সেই অনুপাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়নি। ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হয়নি। এ কারণে মানুষ ক্রমাগত বেকার থেকে দারিদ্র্যের দিকে ধাবিত হয়েছে। তৃতীয়ত, ২০২১ সালের পরবর্তী সময়ে কোভিড মহামারি যখন আস্তে আস্তে বিদায় নিচ্ছিল তখন কৃষিখাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তুু কৃষিখাতে মজুরি হ্রাস পাওয়ার কারণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কর্মসংস্থান জীবনযাত্রাকে উচ্চতরে নিয়ে যেতে পারেনি। ফলে দারিদ্র্য ক্রমাগত বেড়েছে।
যে কোনো অর্থনীতিতে দারিদ্র্য হ্রাসের সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে ক্রমাগত কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা। বিশেষ করে শিল্পখাতে মজুরি অধিক হওয়ায় কারণে শিল্পে যদি কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা যায় তবে দারিদ্র্য হার বৃদ্ধি পায় না। কিন্তুু ২০২২ সালের পরবর্তী সময়ে তা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে বেকারত্বের হার বেশি। আবার এর পিছনেও অনেক কারণ আছে। বাংলাদেশে শিক্ষার বিষয়বস্তুুতে প্রাসঙ্গিকতার অভাব রয়েছে। আবার শিক্ষার মানও নিম্ন। বাস্তবতা বিবর্জিত শিক্ষা কর্মক্ষেত্রে তেমন প্রভাব ফেলতে পারে না। নিয়োগকারীদের চাহিদা মোতাবেক সাধারণ শিক্ষার পাঠ্যক্রম যদি করা হতো তবে তাতে বাস্তবমুখী শিক্ষা পাওয়া যেত। এ দেশের উচ্চ শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষকেরা বিদেশ থেকে ডিগ্রি এনে বিদেশি পাঠক্রমের সাথে সম্পর্ক রেখে নিজ নিজ পাঠ্যক্রম তৈরি করে। কিন্তুু এ দেশের অর্থনীতি হয় অনুন্নত, ফলে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে শিক্ষিত জনশক্তি বাস্তবমুখী কর্মসংস্থানে নিয়োগ পায় না। আবার শিক্ষার মানও অতি নিম্ন। তাছাড়া এদেশে শিক্ষার মান নির্ধারণ করা হয় ইংরেজি জানার ওপর। অথচ সমগ্র উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করা হয় প্রায় বাংলা মাধ্যমে। ইহাই হলো কর্মসংস্থান লাভের বিশাল গলদ। কারণ কর্মসংস্থান লাভের প্রধান দক্ষতা মনে করা হয় ইংরেজি জানাকে। এ ক্ষেত্রে কোনো কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি হয়ত স্বীকার করবেন না। কিন্তুু ইহাই সত্য এবং ইহাই বাস্তব। ফলে উচ্চ শিক্ষিতরা প্রায় বেকার থাকে। আর বেকার মানেই দারিদ্র্যের গভীরতা বৃদ্ধি পাওয়া।
লেখক : প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট; অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, গাছবাড়ীয়া সরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম