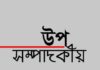অনুপম সেন ৮৪ বছরে পদার্পণ করেছেন। তাঁর জন্ম ১৯৪০ সালের ৫ আগস্ট। দীর্ঘজীবন ধরে তিনি যেমন জ্ঞানের সাধনা করে যাচ্ছেন তেমনি বর্ণাঢ্য তাঁর কর্মময় জীবনও। সত্য ও বিশ্বাসকে আত্মীকৃত করে তিনি পথ চলছেন। তাই আদর্শিক প্রশ্নে তিনি নিরেপেক্ষ নন এবং এখনও শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন এবং তা বিনির্মাণে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর বহুমুখী জ্ঞান এবং বহুমাত্রিক কর্ম তাঁকে অনন্যতায় নিয়ে গেছে। বিগত শতকের ষাটের দশক থেকে স্বকাল–লগ্ন হয়ে বাঙালি মনীষায় প্রাতিস্বিকতায় উজ্জ্বল হয়ে আছেন অনুপম সেন।
অনুপম সেন স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ছাত্রজীবন শেষে তিনি প্রথমে যোগ দেন বুয়েটে। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এরপর তিনি যোগ দেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব বিভাগে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অবসর নেন ২০০৬ সালে। কিন্তু অবসর বলতে যা বোঝায় তিনি তা আসলে নেননি। এরপর যোগ দেন উপাচার্য হিসেবে প্রিমিয়ার বিশ্বদ্যিালয়ে। আমরা তাঁকে শিক্ষক হিসেবেই জানি এবং মানি। তবে সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত। তিনি সমাজবিজ্ঞানী কিন্তু তারচেয়েও বড় সত্য তিনি সমাজকর্মী। লেখালেখিকে কেবল পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেননি, করেছেন সমাজ পরিবর্তনের আয়ুধ হিসেবেও।
অনুপম সেনের রাজনৈতিক চিন্তা থেকে তাঁর সাহিত্য চিন্তা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এবং তা একই ধারায় প্রবাহিত। কবিতা লেখা অব্যাহত না রাখলেও কবিতার অনুবাদ তিনি করেছেন এবং দেখা যায় তাঁর রচনার মধ্যে প্রায়ই তিনি রবীন্দ্রনাথ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। একজন সমাজবিজ্ঞানীর এভাবে সাহিত্যচর্চার কারণ কী? কারণ তিনি মনে করেন সাহিত্য সমাজ–সভ্যতা এবং তার বিকাশ এবং বিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত। সাহিত্যকে তিনি সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করার ফলে তার সাহিত্যচিন্তা আলাদা মর্যাদা লাভ করেছে। যেমন, রবীন্দ্রনাথের ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার মধ্যে একজন কৃষকের যেমন সর্বস্ব হারানোর কথা রয়েছে তেমনি আবার সর্বস্ব হারানোর কারণের ইতিহাসটাও আছে। অনুপম সেন এ ইতিহাসটা দেখেন। এ কবিতার মধ্যে সমাজবিবর্তনের যে ইতিহাস রয়েছে তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষকে তিনি বিচ্ছিন্ন প্রাণী হিসেবে দেখেন না। দেখেন সামাজিক প্রাণী হিসেবে। এবং এ সমাজ বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বিবর্তিত হয়ে আগ্রসর হয়েছে। মানুষ প্রতিটি সমাজ বিবর্তনে উন্নত সমাজ–ব্যবস্থায় উন্নীত হলেও বৈষম্য বরাবরই থেকে গেছে। এবং এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম অনুপম সেনের চিন্তা ও কর্মের একটি মৌল–সত্য।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর জন্ম ফলে বিশ্বযুদ্ধ, মারি ও মন্বন্তর, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ প্রভৃতির মধ্য দিয়েই তাঁর বেড়ে ওঠা। তাঁর জন্ম এবং বেড়ে ওঠার সময়টা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে ছিল ঘটনাবহুল এবং গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্রজীবন থেকে মার্কসবাদ তাঁর চেতনা এবং বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলকে আলোড়িত এবং অনুপ্রাণিত করেছে। তাই ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতা তার চিন্তা এবং কর্মকে প্রভাবিত করেছে সন্দেহ নেই। সমাজ বিবর্তন, সমাজ অগ্রগতিকে তিনি কেবল সমাজদ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে নয়, দেখেছেন শ্রেণিদ্বন্দ্বের ভিতর দিয়েও। মার্কসীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ অনপম সেন শ্রেণি বৈষম্যের বিপরীতে সমতাভিত্তিক সমাজ কামনা করেন। মানব মুক্তির প্রশ্নে তিনি সমাজতন্ত্রের উত্থানই কামনা করেন। ব্যক্তি মালিকানার বিপরীতে সামাজিক মালিকানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণই তাঁর অন্বিষ্ট।
সমাজবিবর্তনের এক পর্যায়ে মানুষ তার শ্রেণি নিরেপক্ষতা হারায়। শ্রেণি নিরপেক্ষতা হারানোর ফলে বৈষম্য শুরু হয়। এবং বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে তা চরম আকার ধারণ করেছে। মূলত প্রথম এলিজাবেথের সময় (১৫৩৩–১৬০৩) ব্রিটেন পুঁজিবাদে প্রবেশ করতে শুরু করে। তারপরের ইতিহাসটা হত্যা, লুণ্ঠন, দেশ দখল এবং শোষণের ইতিহাস। এই পর্যন্ত মানবজাতি তার যে সমাজটা পার করে এসেছে তা ছিল অসাম্য এবং বৈষম্যে ভরপুর। মাঝখানে ৭২ বছর রাশিয়ায় এবং ৭২ দিন প্যারিসে (১৮৭১) ছাড়া। এমনকি সাম্য মৈত্রী, স্বাধীনতার স্লোগান দিয়ে যে ফরাসি বিপ্লব সম্পন্ন হয় সে বিপ্লবও সমতা আনতে পারেনি মানবজাতির জন্য। ফলে সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের যে স্বপ্ন মানুষ দেখে আসছে তা স্বপ্নই থেকে গেছে। অনুপম সেন বলেছেন, ‘কৌম সমাজ থেকে পুঁজিবাদ পর্যন্ত– এই যে দীর্ঘ পরিক্রমা–এ পরিক্রমার মধ্যে শ্রেণি ছিল এবং এ শ্রেণির জন্যেই অসাম্য বজায় ছিল। তিনি আরও বলেন,‘পাশ্চাত্যে কৌম সমাজ ভেঙে যখন রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় এবং এসব রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে উৎপাদন ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তন হয়, সে বিবর্তনে আমরা মুখ্যত তিনটি ঐতিহাসিক স্তর দেখি; দাস সমাজ, সামন্ত সমাজ ও পুঁজিবাদ। তিনটি স্তরের প্রতিটি স্তরে আমরা দুটি মুখ্য শ্রেণি পাই: দাস–প্রভু বনাম দাস, সামন্তপ্রভু বনাম ভূমিদাস বা কৃষক এবং পুঁজিপতি বনাম শ্রমিক।’ (অসাম্যের বিশ্বে সাম্যের স্বপ্ন) এবং এ–শ্রেণিবিভক্তি মানুষের মহামিলনের পথকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে।
২.
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমাজবিবর্তনের মধ্যে স্পষ্টতই প্রার্থক্য ছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেও ছিল মৌলিক পার্থক্য। কারণ, প্রাচ্যের উৎপাদন ব্যবস্থা পাশ্চাত্যের মতো দাস বা ক্রীতদাসভিত্তিক ছিল না। ছিল কৃষিভিত্তিক, গ্রামভিত্তিক এবং প্রতিটি গ্রামই ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর। সাম্রাজ্যের উত্থান–পতন হয়েছে, রাজা এসেছে রাজা গিয়েছে কিন্তু ভারতে এ গ্রামীণ ব্যবস্থা, এ উৎপাদন ব্যবস্থা বজায় ছিল। এ কারণে এ দেশে কে রাজা হলো আর কে নৃপতি হলো তা গ্রামীণ এ মানুষগুলোকে তেমন আলোড়িত করতো না। কিন্তু হাজার বছরের এ গ্রামীণ ব্যবস্থাকে, এ উৎপাদন প্রণালীকে ইংরেজরা এসে পুরোপুরি ভেঙে দেয়। শুধু তা নয়, ইংরেজরা এখানে ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা সৃষ্টি করে পুঁজিবাদের উত্থান এবং বিকাশকেও ত্বরান্বিত করেছে। অনুপম সেন বলেছেন, ‘প্রাচ্যের বিভিন্ন সমাজে, যেমন–আমাদের উপমহাদেশে অনেক দাস ছিল, ক্রীতদাস ছিল। কিন্তু উৎপাদনব্যবস্থা দাসভিত্তিক ছিল না, ছিল মুক্ত স্বাধীন কৃষক, গ্রাম–ভিত্তিক। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল মুক্ত স্বাধীন কৃষক এবং তাদের সাহায্যকারী মুক্ত স্বাধীন কারিগর। এমনকি ইংরেজরা যখন আমাদের দেশের শাসনভার গ্রহণ করে, তখনো এ ধরনের গ্রাম দেখে তারা এসব গ্রামকে Little republic বা ছোট ছোট প্রজাতন্ত্র হিসেবে অভিহিত করেছে।’ (অসাম্যের বিশ্বে সাম্যের স্বপ্ন) ইংরেজপূর্ব এ হাজার বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে বলা যায়, এখানে উপরিকাঠামোগত কিছু পরিবর্তন হলেও ‘মৌল অর্থনীতিতে কোনো বৃহৎ আলোড়ন হয়নি।’ আবার গ্রিস, রোমান সাম্রাজ্যের মতো প্রাচ্যে কৃষিতে দাস–শ্রম মুখ্য ছিল না। তবে উৎপাদনে গতি সঞ্চারিত না হওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে ড. সেন মনে করেন শ্রেণি–সংঘাতের অভাব ছিল। এবং এর ফলে ‘নতুন প্রযুক্তি, নতুন জ্ঞানেরও বিকাশ ঘটেনি।’ তার মানে এই নয় যে, অসাম্য ছিল না। অসাম্য ছিল তবে তা ভিন্নভাবে ছিল। এ অসাম্য নিষ্ঠুরভাবে প্রদর্শিত হয়েছে বর্ণপ্রথায়। বলা হয় ভারতে ক্লাস স্ট্রাগল ছিল না, কিন্তু কাস্ট স্ট্রাগলটা ছিল। ফলে পাশ্চত্যে যেভাবে বণিক পুঁজি সংহত হয়ে পুঁজিবাদের বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছিল প্রাচ্যে সেরকম পুঁজিবাদ বিকশিত হয়নি।
অসাম্য দিন দিন বাড়ছে। এর কারণ ব্যক্তিপুঁজি। ব্যক্তির কাছে সম্পদ বাড়ছে ক্রমাগত। ব্যক্তিসম্পদ পুঞ্জিভূত হচ্ছে। পুঞ্জিভূত হতে হতে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ২০১৮ সালে অক্সফাম জানিয়েছে, ‘২০১৭ সালে সম্পদ বৈষম্য আরও বেড়ে যাওয়ায় বিশ্বের মাত্র এক শতাংশ লোকের হাতে বিশ্বের ৮২ শতাংশ সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়েছে।’ যতই দিন যাচ্ছে এ বৈষম্য বাড়ছে। আবার পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ সংকটও প্রকট আকার ধারণ করছে। কিন্তু ‘এ অসাম্যময় বিশ্ব কারও কাম্য হতে পারে না। হাতে গোনা কটি বহুজাতিক করপোরেশন ও লাখ খানেক লোক বিশ্বের অধিকাংশ সম্পদ কুক্ষিগত করে রেখেছে।’ অনুপম সেনের দৃঢ় বিশ্বাস এ সংকট থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ। সম্পত্তির সামাজিকীকরণ। বিশ্বায়ানের এ সময়ে পুঁজিবাদের এ লোভনীয় সময়েও, তিনি সাহস নিয়ে বলতে পারেন, মানুষের সার্বিক মুক্তির প্রশ্নে সাম্যবাদের উত্থান ছাড়া বিকল্প নেই ।
লেখক– সহকারী অধ্যাপক, বাংলা, সরকারি কমার্স কলেজ, চট্টগ্রাম