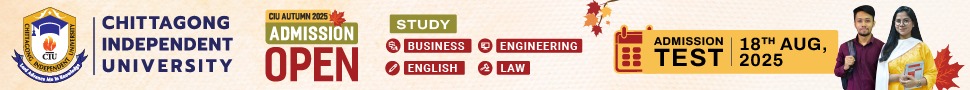সৃষ্টিকর্তা কিছু মানুষকে পৃথিবীতে পাঠান– তাঁদের জ্ঞান, স্বভাব, ব্যবহার ও আচার ধর্মের মাধ্যমে তাঁরা যেন সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র ও বিশ্বকে অনেক কিছু দিতে পারেন। তার ব্যতিক্রম নন প্রফেসর ড. আবদুল করিম। ১লা জুন ২০২৮ সালে বাঁশখালীর সাগর পাড়ের কাছাকাছি অঞ্চল চাপাছড়ির এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ড. আবদুল করিম।
বাংলার ইতিহাসের যুগসমূহের মধ্যে মধ্যযুগই ছিল তাঁর গবেষণার মূল ক্ষেত্র। এ যুগের শিল্পপাঠ ও সমসাময়িক সাহিত্য ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে তিনি প্রবন্ধ ও গবেষণাপুস্তক রচনা করেন। এ ধারায় মুদ্রাতত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত ‘কর্পাস অব দি মুসলিম কয়েনস অব বেঙ্গল’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এ সময়ই তিনি স্থাপত্য ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে রচনা করেন ‘ঢাকা দি মুঘল ক্যাপিট্যাল‘। তাছাড়া শিলালিপিতত্ত্বের কাজ করতে গিয়ে রচনা করেন ‘কর্পাস অব দি এ্যারাবিক এ্যান্ড পার্সিয়ান ইন্সক্রিপশনস অব বেঙ্গল’। এভাবে তাঁর গবেষণায় মধ্যযুগের প্রতিটি ক্ষেত্র বিশেষভাবে পরিধৃত হয়েছে। অসংখ্য গবেষণালব্ধ পুস্তক ও শত শত প্রবন্ধে বাংলার মধ্যযুগকে তিনি বাঙময়তা দান করেছেন।
প্রফেসর ড. আবদুল করিম উপমহাদেশের প্রথম কাতারের ঐতিহাসিক শুধু নন একজন সফল জীবনীকারও। তাঁর রচিত জীবনীসমূহের মধ্যে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ: জীবন ও কর্ম শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। সকল শিক্ষক যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যেমন গবেষক হতে পারে না তেমনি সকল পণ্ডিত ব্যক্তি পাহাড়সম পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েও লেখালেখি বা রচনায় হাত দিতে পারেন না।
প্রফেসর করিম সেদিক থেকে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। তিনি একদিকে যেমন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী অধ্যাপক, অপরদিকে তেমনি গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রণেতা ও মূল্যবান প্রবন্ধ রচয়িতা। তাঁর লেখায় সহজ সরল সরস ভাব ইতিহাসের কঠিন দেয়াল ভেদ করে প্রতিটি পাঠককে সে সময়ের আবর্তে দাঁড় করিয়ে দ্রুত বোধগম্য করতে সাহায্য করে। বিষয় বৈচিত্র্যের এই অনন্যতা অন্য ঐতিহাসিক বা গবেষক বা প্রত্নতত্ত্ববিদ বা শিলাতত্ত্ববিদ থেকে তাঁকে আলাদা করেছে। সেখানেই তাঁর অধিষ্ঠান সেখানেই তিনি প্রফেসর করিম। প্রচণ্ড ধৈর্যশক্তি, প্রগাঢ় মেধা, অতুলনীয় মননশীলতা, ঈর্ষণীয় কর্মসম্পৃহা, গভীর পাণ্ডিত্য সস্নেহ অভিভাবক, স্নেহশীল শিক্ষক–উপদেশক, প্রীতিময় সহকর্মী, শক্তিমান প্রশাসক এবং সর্বোপরি বিরামহীন কর্মযোগী আলোর পুরুষ ড. করিম ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, একটি অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত।
প্রফেসর করিমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা তাঁকে অসাধারণ করে তুলেছে। গ্রামে যাঁর শিকড় অজপাড়াগাঁয়ে যার বেড়ে উঠা তাঁর স্বজন, পরিচিত বা বন্ধুশ্রেণীর মধ্যে কেউ কেউ তার সমবিত্তের বা অবস্থানের অধিকারী না হলেও তিনি তাঁদেরকে একই কাতারের মানুষের মতো আপন করে রেখেছেন ও চাকুরীর ব্যবস্থায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন। যেমনভাবে স্বস্নেহে একান্ত কাছে টেনে নিয়েছেন তাঁর ছাত্রদের ও প্রিয়ভাজন গবেষকদের। পড়িয়েছেন জ্ঞান, মেধা ও উপদেশ দিয়ে তার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছেন, অনেক সময় অনেকের জন্য কোন সম্মানি ব্যতিরেকেও। তিনি ছেলেবেলা থেকেই কিছুটা ধর্মভীরু ছিলেন এবং ধর্মের প্রতি তাঁর আসক্তি ছিল নিরবচ্ছিন্ন। তিনি মধ্যবয়সে বিভিন্ন পীর–দরবেশের সান্নিধ্যে এসে তাঁদের জীবনাদর্শ ও উপদেশাবলী জনসমক্ষে উপস্থাপন করে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। ধর্মের কোন গোড়ামি তাঁকে স্পর্শতো করেইনি বরং তিনি তা ঘৃণা করতেন।
প্রফেসর করিমের আচার–আচারণে অহংবোধের কোন স্থান ছিল না। তিনি অত্যন্ত সাধারণ জীবন যাপন করতেন। আহার–বিহারেও সাধারণ্যে প্রচলিত ধারা ও খাবার গ্রহণ করতেন। বড়লোকী কোন স্বভাব তাঁকে কখনো স্পর্শ করেনি। এই মাটি বা শিকড়ের সন্ধান করতে গিয়ে তিনি মধ্যযুগের জীবনমান—সাহিত্য সংস্কৃতি ও চলমানতার প্রতি যত্নবান হয়েছেন। তাই তাঁর লেখায় মুসলিম ঐতিহ্য ফিরে এসেছে মুসলিমদের আগমন, বিজয়, ইসলাম প্রচার, সুফীদের অবদান অত্যন্ত জোরালোভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর লেখা চট্টগ্রামের ইতিহাস গ্রন্থে বার আউলিয়ায় ও বদর শাহ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। তিনি গরীবউল্লাহ শাহ–এর চট্টগ্রাম আগমন ও আধ্যাত্ম উৎকর্ষতা নিয়ে আলোকপাত করেছেন এবং কোর্ট বিল্ডিং–এ প্রাপ্ত সম্রাট আওরঙ্গজেবের একটি ফরমানের আলোকে মিসকিন শাহের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি শহর কুতুব হযরত শাহ আমানত (র.) সম্পর্কেও একটি পুস্তক লিখেন। তাছাড়া তিনি মাইজভাণ্ডার শরীফ গিয়ে উপমহাদেশের প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক পুরুষ গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী ও বাবা ভাণ্ডারী সম্পর্কে সামগ্রিক অবগত হয়েছেন এবং গাউসিয়া হক মন্্জিল কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকা ও শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)’র উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন।
তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু পুরস্কারপ্রাপ্ত গবেষক। বাংলা ভাষায় ২০টি, ইংরেজি ভাষায় ৮/১০টি পুস্তকসহ দেশ বিদেশের বিভিন্ন উচ্চ মানের সাময়িকীতে ৭২টি গবেষণা প্রবন্ধ ১১২টি বাংলা প্রবন্ধ ও বাংলা একসাইক্লোপিডিয়ার জন্য ১২০টি প্রবন্ধ সংযুক্তি প্রকাশিত হয়েছে এবং ১৯৯৫ সালে তিনি একুশে পদকে ভূষিত হন।
এই মাটি বা শিকড়ের টানেই তিনি দেশের প্রতি অবিচল ভালোবাসা পোষণ করেন। ১৯৬২ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এ্যান্ড আফ্রিকান স্টডিজ–এ অধ্যয়নরত অবস্থায় তাঁর দ্বিতীয় পি–এইচ.ডি লাভের পর কর্তৃপক্ষ সেখানে থেকে যাবার প্রস্তাব করলে তিনি তাতে সম্মত না হয়ে যথাসময়ে ফিরে এসে তাঁর পূর্বের কর্মস্থল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। এছাড়া, মুক্তিযুদ্ধ প্রস্তুতিকালীন সময় যুদ্ধকালীন সময়ে তাঁর অবস্থানের কথা সুবিদিত। তিনি বিনাসম্মানীতে গবেষণা উপদেশক হন, গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, ঝপযড়ষধৎংযরঢ় নিয়ে বিদেশ গিয়ে ফিরে আসেন, প্রতিদিন ক্লাশ নেন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান না, ঘএঙ’র উপদেষ্টা বা ঈঙঘঝটখঞঅঘঞ হন না বা মাসের পর মাস ছুটিতে থেকে বিদেশে অবস্থান করে অন্য ব্যবসা চালাননি।
লেখাটি শেষ করার পূর্বে সে সময়ের তিনজন খ্যাতিমান অধ্যাপক যাঁদের মধ্যে দু’জন তাঁর ছাত্র ছিলেন সহকর্মী হয়েছিলেন পরে উপাচার্য ছিলেন আর অপরজন পৃথিবী জোড়া ব্যক্তিত্ব, তাঁদের লেখায় ড. করিমকে দেখি– প্রফেসর রফিকুল ইসলাম চৌধুরী লিখেন, ড. করিমের ক্লাশের ছাত্ররা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। তিনি সদা সর্বদাই একজন আদর্শ শিক্ষক ও একনিষ্ঠ গবেষক হিসাবে ছাত্র ও সহকর্মীদের নিকট মহাসম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন…মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রতিরোধ গড়ে তোলার সময়ে তার অবদান প্রশংসনীয়। বিভিন্ন সিদ্ধান্তে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও একজন নীতি নির্ধারক হিসাবে অগ্রণী ভূমিকা সম্পর্কে সে সময়কার উপাচার্য ড. এ আর মল্লিক তার লিখিত স্মৃতি কথায় অতি শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করেছেন। প্রফেসর মোহাম্মদ আলী বলেন, “আমি যখন প্রথম বর্ষের ছাত্র তখন ড. করিম বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক… হলের হাউস টিউটর। হাউস টিউটরদের সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিল যথেষ্ট সৌহার্যপূর্ণ– রাত দশটার পরে পালাক্রমে তাঁরা আমাদের হাজিরা নিতেন– আমাদের আপনি বলে সম্বোধন করতেন।… চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্নে যে সাতজন শিক্ষককে নিয়ে উপাচার্য ড. এ আর মল্লিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করেছিলেন আমরা ছিলাম সে সাতজনের দু’জন পরে ১৯৭৫ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৮১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত তিনি উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন।” প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম লিখেন, “ড. আবদুল করিমের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৮০ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ওরিয়েন্টেল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজ এর। আমি দেশে ফিরে আসতে চাই শুনে বলেন, আমি অবশ্যই সাহায্য করব। ড. করিম যখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন উনার আদেশেই আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পাই।” এ তিনজন মহৎপ্রাণ বিদ্বজনকে দিয়ে আমরা প্রফেসর ড. করিমকে দেখতে চেষ্টা করলাম।
লেখক : প্রাবন্ধিক, অধ্যাপক