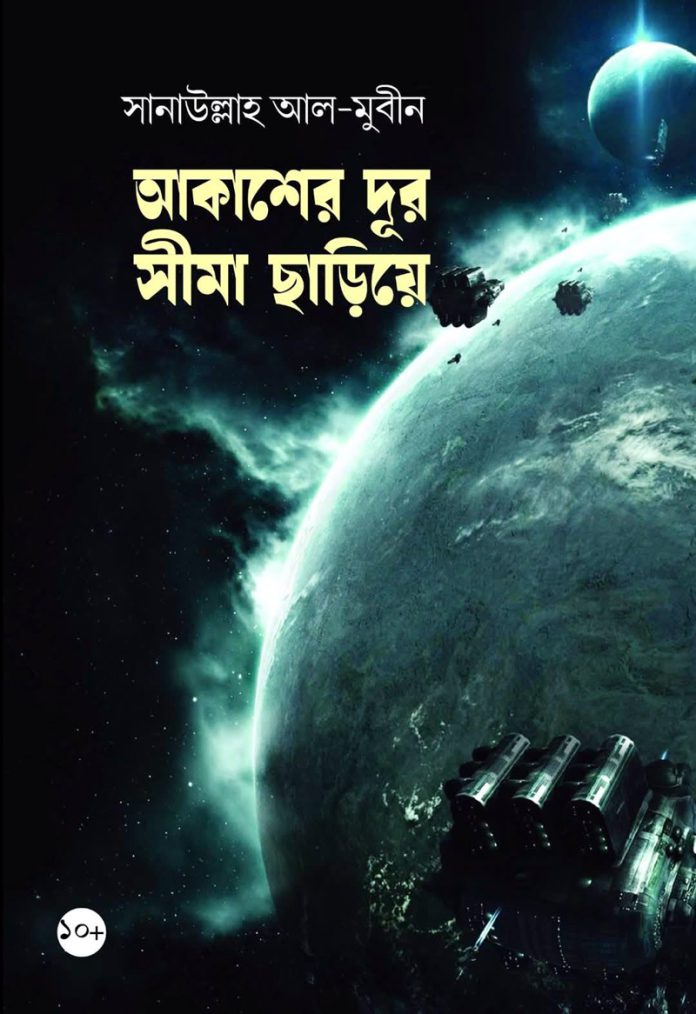অনেকেই বলেন, বিজ্ঞানের ভাষা কাটখোট্টা, এর ভেতরে কোনো রসকষ নেই। পাঠক নিরুৎসাহিত হন বিজ্ঞানবিষয়ক বইপাঠে। কথাগুলোর সঙ্গে আমি একমত। তবে ‘আকাশের দূর সীমা ছাড়িয়ে’ শীর্ষক মহাকাশবিজ্ঞানের ওপর লেখা বইটি পড়ে আমার তেমনটি মনে হয়নি। আমরা যে বাংলা বিজ্ঞান–সাহিত্যের কথা বলি, ঠিক সেই ধাঁচের বইটি।
বইটিতে রয়েছে মোট দশটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধগুলো হলো ১. চাঁদ উঠেছে ওই, ২. ভোর আকাশের তারা, ৩. মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যে, ৪. আকাশের পড়ন্ত তারারা, ৫. শতাব্দীর অতিথি, ৬. মহাবিশ্ব, ৭. আতশবাজির খেলা আকাশে আকাশে, ৮. কৃষ্ণবিবর : মহাকাশের সুড়ঙ্গ, ৯. আইনস্টাইনের বিশ্ব ও ১০. আকাশের দূর সীমা ছাড়িয়ে। নিম্নে একে একে প্রবন্ধগুলোর বিষয়বস্তুর সঙ্গে আমরা পরিচিত হব:
প্রথম প্রবন্ধে চাঁদের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন: ‘পশ্চিমের আকাশ এক অপরূপ রক্তিম আভায় ভাসিয়ে দিয়ে একটু আগে সূর্য ডুবে গেছে। দিগন্ত এখনো লাল টকটকে। আবিরের মতো। রুপোলি রথে চড়ে পুব–আকাশে সহসা উঠে এলো বিশাল থালার মতো চাঁদ, পুর্ণিমার সাদা চাঁদ। বেশ কিছু তারা ফুটে উঠেছে আশেপাশে। আকাশ যেন হীরের চুমকি–বসানো শাড়ি পরেছে গায়…।’ এখানে লেখক অপরূপ ভঙ্গিমায় চাঁদের বর্ণনা করেছেন।
দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে ‘ভোর আকাশের তারা’র কথা বলতে গিয়ে তিনি শুকতারার বর্ণনা করেছেন এভাবে: ‘ক্রমে আকাশ যতই ফরসা হবে, আশেপাশের অন্যসব তারা অদৃশ্য হয়ে যাবে। কিন্তু এই তারাটি তারপরও জ্বলজ্বল করবে, উজ্জ্বল রুপোলি চাকতির মতো…।’
তৃতীয় প্রবন্ধে মঙ্গলের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা উপন্যাসের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। বলেছেন: “শেষের কবিতার নায়ক–নায়িকার মতো অন্য কোনো অমিত ও লিলির কিংবা লাবণ্যর পক্ষে ‘মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যের ছায়ায়’ অথবা ‘তার কোনো–একটা হাজার–ক্রোশী খালের ধারে’ দেখা হয়ে যাওয়াটা হয়তো অসম্ভব নয়।”
চতুর্থ প্রবন্ধে তিনি উল্কার কথা বলেছেন গল্পের ছলে, ছোট্টমণিদের সঙ্গে নিয়ে। লেখক বলেছেন: ‘হেমন্তের শুরুতে সুরভিদের ছোট্ট ধবধবে উঠোনটি ভরে উঠবে সোনালি ধানের মন উতল করা গন্ধে। জোছনাধোয়া রাতে ওরা বেরোবে উঠোনে। বসবে ধানের গাদার ওপর। পাশের বাড়ি থেকে আসবে খুকুমণিরাও। দেখতে দেখতে ওরা গল্পের আসর জমিয়ে তুলবে। ওদের মাথার ওপরে তারার চুমকিবসানো বিশাল এক গোল গম্বুজ। সেখানে রুপোলি চাঁদ হাসবে মিটিমিটি, ওদের দিকে চেয়ে–চেয়ে। খানিক পরে সাদা জোছনার বুক চিরে একটি তারা হয়তো প্রচণ্ড বেগে ছুটে যাবে আকাশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত।’ এই প্রবন্ধটি পড়তে পড়তে আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম জীবনানন্দ দাশের কবিতায়। স্বাদ পাচ্ছিলাম এক অন্য রকম আবেশের।
পঞ্চম প্রবন্ধটিতে ধূমকেতুকে ‘শতাব্দীর অতিথি’ হিসেবে পরিচয় করে দিয়েছেন লেখক। তিনি বলছেন: ‘সন্ধ্যার আকাশকে অপরূপ এক রক্তিমায় রাঙিয়ে… সূর্য পশ্চিম দিকে ডুবে যায়। একটি–দুটি তারা ফুটে ওঠে আকাশের পটে। অন্ধকার ধীরে–ধীরে তার কালো ডানা মেলে দেয় আকাশময়। দেখতে দেখতে তারাদের মেলা বসে যায় সেখানে। দেখে মনে হয়, যেন অসংখ্য তারার ফুল ফুটে আছে আকাশের বাগানে।… মাঝে মাঝে হাসে মায়াবী চাঁদ। জোছনায় ভেসে যায় পৃথিবী।… তারার চুমকিবসানো এই কালো আকাশের পটে কখনো কখনো ওঠে লেজওয়ারা তারা।… এ রকম লেজওয়ালা তারাদের বলা হয় ধূমকেতু : ধোঁয়ার নিশান।… গ্রহ–উপগ্রহরা যেমন সূর্য থেকে ধারকরা আলো নিজেদের শরীর থেকে ঠিকরে দিয়ে গৌরি দীপশিখা হয়ে আকাশে জ্বলে, এরাও তেমনই সূর্যের আলোতেই আলোকিত হয়।’
ষষ্ঠ প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে ‘মহাবিশ্ব’ নিয়ে। লেখক বলছেন: ‘তারারা মহাবিশ্বের সন্তান। এখানে এরা জন্মায়, শৈশব ও কৈশোর কাটায়, যৌবনপ্রাপ্ত হয়, বুড়ো হয়। জীবনের এসব পর্যায় পেরিয়ে তারা এক সময় গিয়ে হাজির হয় মৃত্যুর দরজায়, একদিন তারা মরেও যায়। ছায়াপথে এবং অন্যান্য বিশ্বে, যেমন রযেছে শিশু, কিশোর ও তরুণ তারা, তেমনই রয়েছে প্রৌঢ় ও বুড়ো তারা। আর আছে কিছু মরা তারাও।… যেসব তারা জীবনের মধ্যগগনে গিয়ে পৌঁছোয়, তাদের বলে মূলধারার তারা। আমাদের সূর্য এখন রয়েছে তার ভরা যৌবনে। সুতরাং এটি একটি মূলধারার তারা।’
সপ্তম প্রবন্ধটিতে সুপারনোভার বর্ণনা দিতে গিয়ে ‘আতশবাজির খেলা আকাশে আকাশে’ শিরোনাম ব্যবহার করেছেন লেখক। বলছেন: ‘সূর্যের চারপাশ গ্রহজগতের সৃষ্টি এবং পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ও বিকাশের পেছনে রয়েছে আকাশে দাউদাউ করে জ্বলা অতিকায় দৈত্যতারারা। পূর্বপ্রজন্মের তারারা আকাশে একদিন এভাবে জ্বলেছিল বলেই মহাবিশ্বে সৃষ্টি হতে পেরেছে ভারী মৌলসমূহ। আমাদের সুষমাভরা পৃথিবীর উপাদানসমূহ…।’
অষ্টম প্রবন্ধে লেখক মহাকাশের সবচেয়ে দুর্বোধ্য জ্যোতিষ্ক কৃষ্ণবিবরের ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথের রাজা নাটকের রাজার কথা দিয়ে: ‘যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার তাঁর আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে একটি জায়গায় রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে, ঠিক যেন তেমনই।’
নবম প্রবন্ধটিতে ‘আইনস্টাইনের বিশ্ব’ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শুরুতেই টেনে এনেছেন রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি: ‘আমরা এমন একটা জগতে আছি যার আয়তনের স্বভাব অনুসারেই প্রত্যেক বস্তুই প্রত্যেকের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য। বস্তুমাত্র যে–আকাশে থাকে তার একটা বাঁকানো গুণ আছে, মহাকর্ষে তারই প্রকাশ। এটা সর্বব্যাপী, এটা অপরিবর্তনীয়। এমন–কী, আলোককেও এই বাঁকা বিশ্বের ধারা মানতে হয়।’
দশম প্রবন্ধের শেষে লেখক বলছেন: [ভয়েজার নভোযান] আকাশের দূর সীমা ছাড়িয়ে সূর্যের মতো অন্য কোনো তারার চারপাশে ঘূর্ণনশীল, পৃথিবীর মতো বসতিময় কোনো–গ্রহে গিয়ে হাজির হয় এবং সেই বহির্গ্রহবাসী কোনো বুদ্ধিমান জীবপ্রজাতি যদি তার [বুকে বয়ে বেড়ানো বাংলাসহ পৃথিবীর পঞ্চাটিরও বেশি ভাষায় রচিত শুভেচ্ছাবাণী, শিশুর কান্নার আওয়াজ, বিভিন্ন প্রাণীর ডাক, নানা ভাষার বেশ কিছু গান, কিছু ভিডিও আর ছবি।] পাঠ উদ্ধার করতে পারে, তবে সেদিন সে জানবে, মহাবিশ্বে পৃথিবী নামের একটি গ্রহেও একদিন ফুটেছিল প্রাণের মুকুল, সেই প্রাণ বিকশিত হয়েছিল, শেষে উদ্ভব ঘটেছিল মানুষ নামের এক মেধাবী প্রজাতির, যে সভ্যতা গড়েছিল; ভাষা আবিষ্কার করেছিল, কবিতা ও গান লিখেছিল; সৃষ্টি করেছিল শিল্পকলা; উদ্ভাবন করেছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি; নাও ভাসিয়েছিল তারার দ্বীপের উদ্দেশে, খুলতে চেয়েছিল বিশ্বরহস্যের ঝাঁপি, জানতে চেয়েছিল মহাবিশ্বের অন্য কোনো প্রান্তে সে ছাড়া অন্য কোনো মেধাবী প্রাণরূপের বিকাশ ঘটেছে কি না।’ এরূপ মন্তব্য টেনে বইয়ের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন লেখক।
আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আবদুল্লাহ আল–মুতী, হুমায়ুন আজাদ প্রমুখের বই পাঠে যেমন বাংলা বিজ্ঞান–সাহিত্যের আনন্দ পেয়েছিলাম, ঠিক তেমনই আনন্দ পাওয়া যাবে এই বই পাঠে। আর যাবেই–বা না কেন? লেখকের মহাকাশবিজ্ঞানে অনুরাগ শিশুবয়স থেকেই। তিনি পড়াশোনা করেছেন বাংলাভাষা ও সাহিত্যে। স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে অধিকার করেছেন প্রথম স্থান। এর চেয়ে বড় কথা হলো, তিনি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন ‘রবীন্দ্রসাহিত্যে বৈজ্ঞানিক উপাদানের ব্যবহার’ শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে। এই বিষয়ে তাঁর একটি প্রকাশিত গ্রন্থও রয়েছে। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন অধ্যাপকও বটে। তাঁর হাত দিয়ে এমন একটি রসালো বিজ্ঞান–সাহিত্যের বই উপহার পাওয়া আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের বইকি।
পরিশেষে বলব, বইটিতে নক্ষত্রমণ্ডল নিয়ে যদি একটি প্রবন্ধ থাকতো, তাহলে নক্ষত্র চেনা সহজ হতো। আশা রাখি বইটি মহাকাশকে জানতে সাহায্য করবে। শুধু শিশু–কিশোর নয়, বড়দেরও ভালো লাগবে বইটি। বইটি প্রকাশ করেছে ‘কাকাতুয়া’। প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি ২০২৫। আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি। লেখক সানাউল্লাহ আল–মুবীনকে জানাই নিরন্তর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন!
লেখক : বিজ্ঞান লেখক; ডেপুটি রেজিস্ট্রার, জামাল নজরুল ইসলাম গণিত ও ভৌত বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়