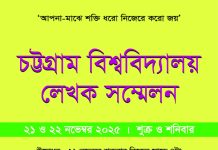শুরুতে মানুষের সভ্যতা – ভব্যতা তৈরি হয় পারিবারিক ধারাবাহিকতায়। মা ও বাবা প্রধানত শিশু – কিশোরদের গাইড। কারণ সন্তানের প্রথম পাঠ শুরু নিজ গৃহ থেকে। ধীরেধীরে বড় হওয়া সন্তান রুচিবোধ শেখে, কথা বলা শেখে। শালীনতা ও সংযমী হতে শিক্ষা গ্রহণ করে। উল্লিখিত ৩টি ভাবানুষঙ্গ রীতিসিদ্ধ হলে রুচিবোধ তৈরি হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় আমাদের অনেকের মধ্যে শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিত্ব ও রুচিবোধের বৈকল্য দেখা যায়। আমরা উদারচিন্তার হতে পারি না। এ–ই হীনচেতা মন আমাদের সমাজ জীবনে, রাষ্ট্রীক জীবনে, এমনি কি ব্যক্তি জীবনেও নঞর্থক প্রভাব ফেলে। অর্থশাস্ত্র বলে, মানুষ রুচিহীন ও স্বার্থান্ধ হয় অর্থনৈতিক লেন দেনে জড়িয়ে গেলে। সে–ই সাথে মানুষ সাংস্কৃতিক গুণপনা ধারণ করা থেকেও বিরত থাকে।
সৃজনশীলতার বড় শক্তি রুচিবোধ এবং নিটোল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। আমাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের জায়গা আজ সংকোচিত। অতএব, সহনশীলতা ও সমপ্রীতি আমাদের রুচিবোধের জায়গা তৈরি করতে পারে অনায়াসে। অনর্থক দম্ভ ও জটিলতার কারণে অনেক মানব সভ্যতার পতন হয়েছে।
একজন মানুষ আধুনিকায়নে নিজেকে যতই প্রস্তুত করুন না কেন, যতই ক্ষমতাধর ভাবুক শিক্ষা ও মানবিক গুণাবলীর সমন্বয় না ঘটালে বুদ্ধিদীপ্ত আধুনিক বিজ্ঞান মনস্ক থাকতে পারে না। যুক্তি দিয়ে, মুক্তি দিয়ে আধুনিক দর্শন চর্চায় মানুষের কথা নিঃসংকোচে বলতে পেরেছেন যে ক‘জন তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট লেখক গবেষক অধ্যাপক ড. আহমদ শরিফ, বিশিষ্ট লেখক ভাষাবিজ্ঞানী, গবেষক কবি হুমায়ুন আজাদ এবং উভয় বাংলার স্বনামধন্য লেখক ঔপন্যাসিক আহমদ ছফা। হুমায়ুন আজাদের সাহিত্য বিষয়ক ক্ষুরধার সমালোচনার মধ্যে ছিলো নতুন আয়না দেখার দর্শন। পর্যাপ্ত ক্ষুরধার যুক্তি ও দেখার নতুন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি। হুমায়ুন আজাদ অহংবোধ আত্মকেন্দ্রিক নার্সিসিজমে আক্রান্ত ঠিকই, তবে মেধার ঘাটতি ছিলনা। অন্যের লেখার ওপর তাঁর আক্রমণ ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের। তিনি ব্যক্তি আক্রমণে বাংলাদেশে অদ্বিতীয় একজন। আবার কঠিন দৃঢ় সংকল্প সঞ্চারিত মনোবল ভাঙেনি এমন বুদ্ধিজীবীদেরও আমরা দেখেছি, যেমন ড. আহমদ শরীফ, তিনি বিজ্ঞান প্রযুক্তি আপাদমস্তক বিশ্বাস করেও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং পুঁথিসাহিত্য সংস্কৃতি তাঁর বাঙালি সমাজ মানস মস্তিস্কের সম্পদ। তিনি খাঁটি প্রথাবিরোধী বুদ্ধিজীবী। তেমনিভাবে আমরা দেখি আহমদ ছফাকে, আধুনিক জীবন দর্শন চর্চা করে নিজের জায়গা পাকাপোক্ত করেছেন বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই করে। তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। তিন জনের চারিত্রিক বিন্যাস একই কাঠামোয় রাগী ও তেজিয়ান স্বভাবের হলেও সৃজনশীল পরিমিতিবোধ শিল্পবোধ সম্পন্ন। তাঁরা ছিলেন লড়াকু সৃজনশীল মানবিক চৈতন্য–সত্তা। দুইজন বিশ্বখ্যাত, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং স্বনামধন্য পণ্ডিত– লেখক। আহমদ ছফা ভবঘুরে ফুলটাইম লেখক। নাট্যকার ঔপন্যাসিক গ্যোতের ফাউস্ট অনুবাদ করার পর জার্মানিতে আহমদ ছফা ফ্যান ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। তাঁরা বলতে গেলে পাবলিক প্রপার্টি। যাঁদের কথা এতক্ষণ বলা হলো তাঁদের নিজস্ব আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা গ্রন্থ রয়েছে। এই পেনিন্সুয়ালার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের টেক্সট দর্শন পড়ানো হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য অনেকের টেঙট নাই। টেক্সটহীনতা সমালোচিতজনকে চিনতে কষ্ট হয়। কবিতা শোনে বা পড়ে বা টেবিল টকে বসে কবি সম্পর্কে জাজমেন্টাল হওয়া সঠিক বিবেচনা নয়। যাদের কোনো টেক্সট নেই, পত্রিকায় প্রকাশিত মৌলিক কোনো প্রবন্ধ নেই। লেখা প্রকাশিত হতে দেখা যাইনি কোথাও সৃজনশীলতার প্রশ্নে তিনি নবিশ কিংবা খোশনবিশ। কিছু বলার অধিকার ও ব্যক্তিত্ব তখনই প্রতিষ্ঠিত থাকে যখন তিনি সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে ওঠেন। যার কথা মান্যযোগ্য সবখানে, নয়তো ক্লাউন হাস্যকর।
ছন্দ কবিতার বিজ্ঞান বা অংক ই বলা চলে। মাপঝোঁক কবি ছাড়া ভালো বেশি কেউ বুঝবেনা। আবার ছন্দ –ই কবিতার একমাত্র মাপকাঠি নয়। অন্যান্য বিষয় সম্পদ নিয়ে একটা ভালো কবিতা হ‘য়ে ওঠে। খালি একটা একটা শব্দ গোনে মাত্রা হয়না। আলোচনার অংকে অনেকেই ভুল করে ফেলে।
আলোচনা স্বতঃস্ফূর্ত না হয়ে জেদি ও একরোখা হয় ভুল হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। ছন্দ আলোচকের ক্লিয়ার ধারণা না থাকলে ছন্দ ছাড়া সাব্জেক্ট নিয়ে কথা বলা বুদ্ধিমানের কাজ। সেই ক্ষেত্রে বুঝতে হবে কবিতার মেটাফোর, সিমিলি, এলিগরিক্যাল আস্পেক্ট। আবার এ–সব ছাড়া শুধু কথনের স্পন্দনে ভালো কবিতার জন্ম হতে পারে। এ–সব কবির এক্তিয়ার। কবিতার সৌন্দর্যজ্ঞান বড় মধুর ঐকতান হতে পারে। সৌন্দর্যতত্ত্ব, যেটিকে এস্থেটিসিজম বলা হচ্ছে কবিতাকে শিল্পোত্তীর্ণ করতে পারে একটা সমৃদ্ধ চিত্রকল্প ব্যবহারে। সামপ্রতিক সময়ে অনেকে এ আই ফরমেট অনুসরণ করে কবিতা ব্যাখ্যায় লেগে পড়েন। কাউকে নিয়ে লিখতে চাইলে চ্যাটজিপিটির বোতাম টিপে লেখা বের করে আনা লেখকের দুর্বলতা। একটি পরিচিত টার্মস নিয়ে মাঝেমধ্যে কথা হয়। থিসিস, এন্টিথিসিস ও সিন্থেসিস নিয়ে এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা পেলাম। এই ধারণা ভীষণ জনপ্রিয়। হেগেলিয়ান দ্বান্দ্িবক ধারণার বিকাশ ও বিবর্তনের ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। ফ্রিডরিখ হেগেল ও ফিচেট যৌথভাবে এই পদ্ধতি অনুসরণ করে মূলত আ্যান্টিথিসিস এর দ্বন্দ্েবর সমাধানে ব্যবহৃত হয়। অ্যান্টিথিসিস একটা থিসিসের সরাসরি বিরোধিতা করে। নিজের মনের মাধুরি মিশিয়ে ব্যাখ্যা করে আরেকটি সমাধানে আসতে হলে এটিকে গবেষণাগারে পাঠাতে হবে। তবে বলা হয় এ–সব টানাপোড়েনে সিন্থেসিস বা সমন্বয় খুব দরকারি।
আমরা ক্রমশই হীনম্মন্যতাবোধে আক্রান্ত। প্রকৃত সৃজনশীলতার চেয়ে নাটুকেপনায় বিশ্বাসী। আমরা পরস্পরকে সহ্য করতে পারছি না। সম্মানিতজনকে সম্মান জানাতে অক্ষম। কাজের চেয়ে আস্ফালন বেশি। অপরের রচনাকে ইচ্ছাকৃত নেতিবাচক সমালোচনা করে কীভাবে ছোট করা যায় তা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। সর্বোপরি, নিজের লেখাটাই শ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা ও চর্চায় রাখছি। জানা ও বোঝার চেয়ে পাণ্ডিত্যের আধিক্য সমাজ রাষ্ট্র পিছিয়ে পড়ছে, অনুধাবনের শক্তি আমরা ক্রমশ হারিয়ে ফেলছি। তদুপরি তরুণদেরও এই শিক্ষায় আচ্ছন্ন করবার চেষ্টা করছি অনবরত। বন্ধুভাবাপন্নতা আমাদের মধ্যে আর অবশিষ্ট নাই। সাহিত্যের জন্য কাউকে পুরস্কৃত করা হলে পুরস্কৃত জনকে তিরস্কারসহ কোনঠাসা করার মহড়ায় ব্যস্ত থাকি। অর্থাৎ রুচি, শিক্ষা, সংস্কৃতির বিন্দুমাত্র শুভবোধ আমাদের মধ্যে নেই। এটি এক রকমের সংকীর্ণ মানসিক দারিদ্র্য ছাড়া আর কী হতে পারে! আবার মানসিক ভারসাম্যহীনতাও বলা যায়। মানসিক বৈকল্য ত্বরান্বিত যার তাকে দিয়ে ভালো ও সুস্থ কিছু আশা করা যায় না। এরা নিজেরাই নিজেদের বিদ্যাভূষণ ভাবে, এরা নিজেরাই ভাবে একেকজন লেনিন, কার্ল মার্ক্স, সক্রেটিস, এরিস্টটল। তাঁরা কবিতার দর্শন নিয়ে যা ভাবছে তার ঊর্ধ্বে কোনো ভাবনা দর্শন থাকতে পারে না। তাদের ভাবনার ঊর্ধ্বে কোনো এস্থেটিক সেন্স থাকতে নেই। একটা আপ্তবাক্য বর্তমান সময়ে প্রায়শই উচ্চারিত: ইন্টেলেকচুয়াল হাইট। এই হাইটেক পার্ক জ্ঞান নিয়ে গদগদকণ্ঠ ইন্টেলেকচুয়ালরা সবখানে বর্তমান।
প্যারাসিটামল ও লিভারের ঔষধ বিক্রি করে হাইটেক মানুষ সমাজ মানসের চিন্তার নায়ক হতে চায়। এদের মধ্যে কবিতার ছন্দ–জ্ঞান বিন্দুমাত্র নাই, অথচ ভান করে যেন একেকজন আব্দুল কাদির, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কিংবা শঙ্খঘোষ। নাক উঁচু ব্রাহ্মণ্যবাদী মনে করা এ–সব উদ্ভট বিকলাঙ্গ নপুংসক চিন্তা চেতনায় আচ্ছন্ন মানুষে ভরে যাচ্ছে দেশ ও সমাজ –রাষ্ট্র কাঠামোতে। বিশ্বে গত শতাব্দীর উনিশ–বিশ শতকে নানা দর্শনের আবিষ্কারের ফলে শিল্প–সাহিত্যে, প্রযুক্তিতে একটা অগ্রসর পৃথিবীকে আমরা দেখতে পেয়েছি। সমাজের আত্মনিমগ্নতা, আত্মবিশ্বাস ক্রমশই দুর্বল করে দিচ্ছে এরা। এরাই মূলত সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত। চিকিৎসার দরকার আছে এদের। নয়তো দেখা যাবে ভর দুপুরে দিগম্বর হ‘য়ে এরা দৌড় দেবে। আর সেটিই হবে লজ্জার – নিচুস্তরের, নিম্নমান জ্ঞান গরিমার। সারাবিশ্ব বলবে আমাদের চিন্তার দারিদ্র রোগেভুগে উঠে দাঁড়াতে শেখেনি।
সমাধান কী? রুচিবোধের শিক্ষা, সাংস্কৃতিক সমনস্ক মানুষের মিলন মেলায় মানবতা সম্মানের বিষয়টি অগ্রাধিকার পাওয়া। বিধ্বংসী খেলা বন্ধ করে সুস্থ ধী–সম্পন্ন মানুষের ইতিবাচক বিস্ময়কর শক্তিকে একত্রিত করা। ব্যাপারটা খুব কঠিন যদিও। সব সমাজে নষ্ট মানুষের আধিপত্য থাকে। মবিস্ট মানুষের আনাগোনা থাকে। তাদের শুদ্ধ করা আমাদের দায়িত্বের অংশ। তাদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি যে কোনো মূল্যে ইতিবাচক করে তোলা আমাদের কাজের অংশ হতে হবে। কাজটা দুরূহ হলেও ঝুঁকি নিয়ে আমাদের অপারেশন ক্লিঞ্জিং এ নামতে হবে। নইলে সৃজনশীল কর্মকাণ্ডকে টাকা পয়সার বিনিময়ে হাবিয়া দোজখ করে দেবে। পরম করুণাময় সবাইকে ধৈর্য ধারণের শক্তি দিক। সৃজনশীলতার শিক্ষা দিক।
লেখক : কবি, প্রাবন্ধিক।