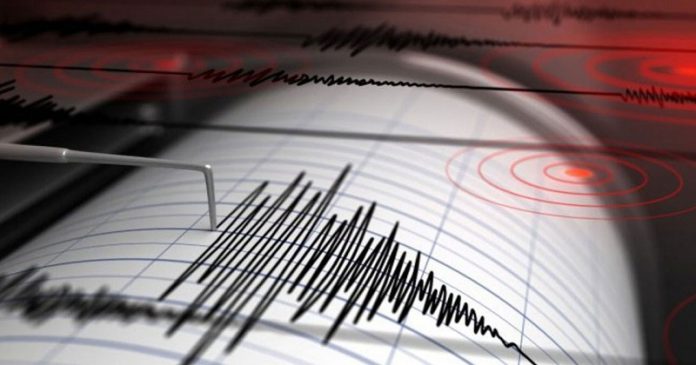দেশের সবচেয়ে ভূমিকম্প ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত আছে চট্টগ্রাম। তাই বড় ধরনের ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে চট্টগ্রামসহ সন্নিহিত অঞ্চল। ভারতীয়, ইউরেশীয় ও বার্মা টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলের নিকট অবস্থানের কারণে এই অঞ্চল ভূমিকম্পপ্রবণ বলেও বিবেচিত। বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুযায়ী, চট্টগ্রামের অবস্থান সিসমিক জোন–৩ এ, যেখানে নকশাগত ভূমিকম্প ত্বরণ তুলনামূলকভাবে উচ্চ ধরা হয়। সাম্প্রতিক সিসমিক হ্যাজার্ড গবেষণাতেও দেখা গেছে, বড় মাত্রার কম্পন হলে নগরীর বিভিন্ন স্থানে ভূমিধসসহ বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।
চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভূমিকম্প ঝুঁকির মূল উৎস এর ভূগাঠনিক অবস্থান। ইন্ডো–বার্মা কোলিশন জোনে ভারতীয় প্লেট পূর্ব দিকে সরে গিয়ে বার্মা প্লেটের নিচে ঠেলতে থাকে। ফলে এলাকায় দীর্ঘমেয়াদি টেকটোনিক স্ট্রেইন জমে। বিজ্ঞানীদের মতে, এই অঞ্চলে একটি বড় ‘মেগাথ্রাস্ট’ সেগমেন্ট লকড অবস্থায় রয়েছে, যা কোনো একসময় মুক্ত হলে ৮ মাত্রা বা তার চেয়েও বড় ভূমিকম্প ঘটতে পারে।
ইতিহাসেও এর প্রমাণ রয়েছে বলে উল্লেখ করে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ১৭৬২ সালের আরাকান–চট্টগ্রাম ভূমিকম্পের আনুমানিক মাত্রা ছিল ৮.৫ থেকে ৮.৮, যা উপকূলীয় এলাকায় ভূমি ধস, উত্থান, নদীতীরে ফাটল এবং সুনামিজাত ঢেউ সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তী সময়ে ভারতের উত্তর–পূর্বাঞ্চল ও মিয়ানমারের একাধিক ভূমিকম্প চট্টগ্রামে মাঝারি কাঁপুনি সৃষ্টি করেছে, যদিও সেগুলোর উপকেন্দ্র দূরে ছিল।
চট্টগ্রামের মাটি ও ভূমির প্রকৃতিও ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। কর্ণফুলী অববাহিকা, উপকূলীয় পলি এবং পূর্ণ ভূমির নরম মাটিতে ভূমিকম্পের সময় মাটির তরলীকরণ ঘটার আশঙ্কা থাকে। বালু মাটি ও পানি সমৃদ্ধ স্তর শক্তি হারিয়ে ‘তরল’ হয়ে গেলে ভবনের ভিত্তি বসে যাওয়ার মতো বড় বিপর্যয় ঘটতে পারে। পাহাড় কাটার কারণে নগরীর অনেক স্থানে ঢাল অস্থিতিশীল হয়ে পড়েছে। ভূমিকম্পের ধাক্কায় এসব স্থানে ভূমিধসের ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি। অতীতে ভারী বর্ষণে যে পাহাড় ধসের ঘটনা ঘটেছে, বড় ভূমিকম্প হলে তা আরো ভয়াবহ আকার নিতে পারে।
নগরায়ণ ও অবকাঠামোগত বাস্তবতাও পরিস্থিতিকে জটিল করেছে। নগরীতে অনেক ভবন অনুমোদন ছাড়া নির্মাণ করা হয়েছে। নকশাবহির্ভূত নির্মাণ অগুনতি। অনেক ভবনই পুরনো। সঠিক সিসমিক নকশা অনুযায়ী নির্মিত ভবনের সংখ্যাও নগণ্য। উচ্চ জনঘনত্বের কারণে দুর্যোগ এবং পরবর্তী রেসকিউ কার্যক্রমও বাধাগ্রস্ত হতে পারে। বন্দর, তেল–ট্যাংক, গ্যাস স্থাপনা, বিদ্যুৎকেন্দ্র, কন্টেনার ইয়ার্ডসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় কম্পনের তীব্রতা বেশি হলে কেবল অর্থনৈতিক ক্ষতি নয়, পরিবেশগত বিপর্যয়ও ঘটতে পারে।
বিজ্ঞানীরা আগামী কয়েক দশকের মধ্যে এ অঞ্চলে মাঝারি থেকে বড় ভূমিকম্প ঘটার আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। প্লেট চলনের হার বছরে গড়ে ৪ থেকে ৫ সেমিতে জমে থাকা স্ট্রেইন যে–কোনো সময় পরিবর্তন হতে পারে। ঝুঁকি কমানোর একমাত্র উপায় হলো বৈজ্ঞানিক প্রস্তুতি, সঠিক নির্মাণ কোড মেনে ভবন নির্মাণ, পুরনো ভবনের সিসমিক মূল্যায়ন ও রেট্রোফিটিং, ঝুঁকিভিত্তিক নগর পরিকল্পনা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি।
চট্টগ্রামের জন্য জরুরি হলো কঠোরভাবে বিল্ডিং কোড অনুসরণ নিশ্চিত করা, মাটি ও ভূমি ঝুঁকির ভিত্তিতে ওয়ার্ডভিত্তিক মাইক্রোজোনেশন মানচিত্র তৈরি, পাহাড় কাটা পুরোপুরি বন্ধ, ঢাল স্থিতিশীল করার ব্যবস্থা গ্রহণ, স্কুল কলেজ হাসপাতাল বন্দর ও কলকারখানায় নিয়মিত ভূমিকম্প মহড়া পরিচালনা এবং দুর্যোগ পরবর্তী রেসপন্স টিমকে সুসংগঠিত রাখা। পাশাপাশি বন্দর নগরীর জন্য বিশেষায়িত ইমার্জেন্সি রেসপন্স পরিকল্পনা প্রয়োজন, যাতে প্রধান সড়ক, সেতু ও প্রবেশপথ দ্রুত পরিষ্কার রাখা যায়।
বিশেষজ্ঞদের মতে, চট্টগ্রাম একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অঞ্চল। বড় ভূমিকম্প হলে এর প্রভাব শুধু স্থানীয় নয়, সারা দেশে পরিব্যাপ্ত হবে। তাই ভূমিকম্পকে দুর্লভ ঘটনা ভেবে অবহেলার সুযোগ নেই। আগাম প্রস্তুতি, বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে নীতি গ্রহণ এবং সচেতন নগরবাসী এই তিনটি উপাদানই চট্টগ্রামকে বড় বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারে।
নগর পরিকল্পনাবিদ স্থপতি আশিক ইমরান বলেন, চট্টগ্রাম বাংলাদেশের সবচেয়ে স্পর্শকাতর সিসমিক জোনগুলোর মধ্যে একটি, কিন্তু নগর পরিকল্পনা ও অবকাঠামো উন্নয়নে সেই ঝুঁকিকে কেন্দ্র করে যে প্রস্তুতি থাকা উচিত, তা এখনো পর্যাপ্ত নয়। শহরের বড় সমস্যা হলো এলোমেলো নগরায়ন, নরম মাটি, পাহাড় কাটা এবং অনুমোদনবিহীন বা সিসমিক নকশাবহির্ভূত ভবন নির্মাণ। এগুলো ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতিকে বহু গুণ বাড়িয়ে দেয়।
তিনি বলেন, শুধু বড় ভূমিকম্প নয়, মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প হলেও ভূমিধস এবং ভবন ধসে পড়ার মতো ঘটনা ব্যাপক প্রাণহানি ঘটাতে পারে। কর্ণফুলী অববাহিকা থেকে পাহাড়ি ঢাল সব অঞ্চলে সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি আছে। কিন্তু আমরা এখনো ওয়ার্ডভিত্তিক মাইক্রোজোনেশন মানচিত্র তৈরি করতে পারিনি। এত বড় একটি মহানগরে ঝুঁকিভিত্তিক পরিকল্পনা ছাড়া টেকসই উন্নয়ন কল্পনাও করা যায় না।
তার মতে, ভূমিকম্পের ঝুঁকি কমাতে এখন সবচেয়ে জরুরি তিনটি পদক্ষেপ হলো, বিল্ডিং কোড অনুযায়ী সকল নতুন ভবনের বাধ্যতামূলক সিসমিক ডিজাইন, পুরনো ভবনের সিসমিক মূল্যায়ন রেট্রোফিটিং এবং পাহাড় কাটার উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ। তিনি বলেন, নগরবাসীকে সচেতন করা, স্কুল–কলেজ ও সরকারি অফিসে নিয়মিত ভূমিকম্প মহড়া চালানো এবং জরুরি রেসপন্স রুট চিহ্নিত করা শহরের জন্য অত্যাবশ্যক। চট্টগ্রামকে রক্ষা করতে হলে পরিকল্পনাভিত্তিক নগর ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই।