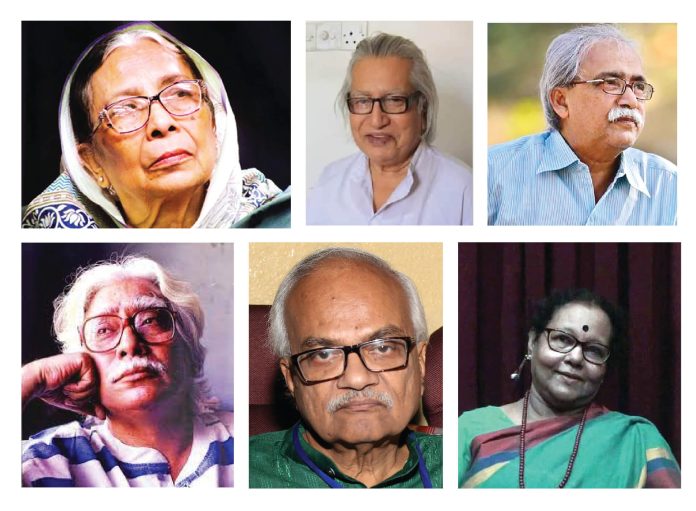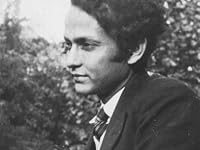(পর্ব ২)
ওই সময়টাতে চট্টগ্রাম শহরের কে.সি.দে রোড এলাকায় ‘হ্যাপি লজ’ ও ‘নভেলটি’ নামে দুটো রেস্তোরাঁয় রাজনীতিক-লেখক-শিল্পীদের আড্ডা বসত। রাজনীতি আর শিল্পী-সাহিত্যের নানা বিষয় ছিল সেখানে একাকার। কারা সেখানে আড্ডা জমাতেন, সেই আড্ডারুদের সব নাম উদ্ধার করা যায়নি অনেকের সঙ্গে কথা বলেও। তবে বাম ধারার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত একদল তরুণ, যাঁরা আবার সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গেও যুক্ত, তাঁরা এ দুটি আড্ডায় নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন বলে শুনেছি। সেই ধুন্দুমার আড্ডার গল্প এখন প্রায় কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে।
ব্যতিক্রমী একটি আড্ডার কথা এখানে না বললেই নয়। সেটা এনায়েতবাজারের মুশতারী লজে ‘বান্ধবী’র আড্ডা। মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ডা. মোহাম্মদ শফি ছিলেন শিল্প-সংস্কৃতিতে নিবেদিতপ্রাণ একজন মানুষ। তাঁর স্ত্রীর নামে বাড়ি মুশতারী লজে নিয়মিত আড্ডা দিতেন স্বাধীন বাংলা বেতারের শব্দসৈনিক বেলাল মোহাম্মদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হাসান ইমাম, তাঁর স্ত্রী নাট্যশিল্পী মনি ইমামসহ বেশ কয়েকজন। এই বাড়ি থেকেই স্বামীর পৃষ্ঠপোষকতায় মুশতারী শফী ‘বান্ধবী’ নামের একটি পত্রিকা বের করার পরিকল্পনা করেন। আসলে তখন পূর্ব-পাকিস্তানের অবাঙালি কর্মকর্তাদের স্ত্রীদের অবকাশ যাপন ও বিনোদনের জন্য যে অভিজাত লেডিস ক্লাব গড়ে উঠেছিল, মুশতারী শফীরা সেখানে যোগ না দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতির ধারাকে বেগবান করার জন্য একত্র হওয়ায় একটা উপায় খুঁজছিলেন। ‘বান্ধবী’ পত্রিকা ও ‘বান্ধবী সংঘ’ সেই বিকল্প। মুশতারী লজে লেখক উমরতুল ফজল, আইনুন নাহারসহ অনেকেই নিয়মিত আসতেন, আড্ডা দিতেন। এঁদের লেখা নিয়েই মুশতারী শফীর সম্পাদনায় প্রকাশিত ‘বান্ধবী’ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল, জনপ্রিয়তাও পেয়েছিল। ‘বান্ধবী প্রেস’ নামে একটি প্রেসও গড়ে উঠেছিল, যার কম্পোজিটর থেকে মেশিনম্যান পর্যন্ত সবাই নারী। মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত আগে এইসব আড্ডাস্থল সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি হয়ে উঠেছিল আসন্ন অসহযোগ আন্দোলন ও মুক্তি সংগ্রামের দিনগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণ নিয়ে নানা উদ্যোগ-পরিকল্পনার কেন্দ্র। এসব তথ্য যেকোনোভাবেই হোক জানা হয়ে গিয়েছিল শত্রুপক্ষের, তাই মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকেই পাক-বাহিনী ঘিরে ফেলেছিল এই বাড়ি। মুশতারী শফী হারিয়েছিলেন তাঁর স্বামী ও সকল সৃজনশীল উদ্যোগের পৃষ্ঠপোষক ডা. শফীকে। মুশতারীর ভাইকেও হত্যা করেছিল পাক-হানাদারেরা। সে এক অন্য মর্মস্পর্শী গল্প।
দেশ স্বাধীন হওয়ার পর চট্টগ্রামের সবচেয়ে বহুল আলোচিত আড্ডাটি ছিল কোতোয়ালী থানার মোড় এলাকায় ‘সাধু মিষ্টান্ন ভান্ডারে’। এই আড্ডা সম্পর্কে নানা জনের বিশেষ কৌতূহলের কারণ ছিল। এখানে যাঁরা আড্ডা দিতে আসতেন, সেই তরুণ লেখক-শিল্পীরা ‘স্পার্ক জেনারেশন’ নামে একটি সাহিত্য আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। যা হয়, দীর্ঘ সংগ্রাম ও প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের পর একটি দেশ স্বাধীন হলে, জনগণের, বিশেষ করে তরুণ সমপ্রদায়ের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা থাকে অসীম। যুদ্ধ ফেরত ‘রাগী তরুণেরা’ তাৎক্ষণিক প্রাপ্তি চায়। প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির গরমিল হলেই ক্ষোভ ও ক্রোধের উচ্চারণে তারা সচকিত করে তুলতে চায় সমাজকে। অনেকের ধারণা, কোলকাতার ‘হাংরি জেনারেশন’ বা ঢাকার ‘স্যাড জেনারেশনে’র একটা প্রভাব কাজ করেছিল স্পার্ক প্রতিষ্ঠার পেছনে। অবশ্য স্পার্কেও অন্যতম পুরোধা কবি স্বপন দত্ত বলেন, ‘আমরা তখন হাংরির নামই শুনিনি।’ যা-ই হোক, সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত ‘স্পার্ক জেনারেশন’ কতটা পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছিল সেটা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু এই নগরে কতিপয় রাগী তরুণের ‘অদ্ভুত’ ‘উদ্ভট’ কিছু ঘোষণা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই।
‘স্পার্ক জেনারেশন প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিবিরোধী প্রগতিশীল সাহিত্য সংস্কৃতি ও শিল্প আন্দোলন। এস্টাবলিশমেন্ট বিরোধিতাই এর মূল উদ্দেশ্য।’ ‘এ ধরনের বোধগম্য লক্ষ্যআদর্শ ঘোষণার পাশাপাশি, যখন ‘বগল-বুক-নাভি-প্রকাশ রমণীর বলিষ্ঠ জংঘায় সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়ে আমরা শিল্পের ম্যাডোনাকে জাগিয়ে দেব’ শ্লোগান উচ্চারণ করা হয়, তখন এই তরুণদের দৃষ্টি আকর্ষণী চমক সৃষ্টির প্রবণতাও প্রকাশ হয়ে পড়ে। ‘সাধু মিষ্টান্ন ভান্ডারে’ ছিল এই তরুণদের আড্ডা। কবি স্বপন দত্ত, শিশির দত্ত, শেখ খুরশিদ আনোয়ার, কাজী রফিক, গল্পকার হেনা ইসলাম, শিল্পী ও গল্পকার সৈয়দ ইকবাল এবং কিছুকাল পর যুক্ত হওয়া কবি আবসার হাবীব ছিলেন স্পার্ক জেনারেশনের ঝান্ডাধারী। স্পার্ক জেনারেশন পত্রিকার ১০ থেকে ১২টি সংখ্যা প্রকাশিত হয় এই সময়ে। এই তরুণেরা শিল্প-সাহিত্যের জন্য অভিন্ন একটি ম্যানিফেস্টো ঘোষণা করলেও, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। ‘সাধু মিষ্টান্ন ভান্ডারে’ অবশ্য স্পার্কের সঙ্গে যুক্ত কবি-শিল্পীরা ছাড়াও অনেকেই আড্ডা দিতে আসতেন। কবি ত্রিদিব দস্তিদার, ফতেহ আলী জুলফিকার, আবু জাফর মনোজ, শ্যামল অদুদ, কাসাহো সাকু, মোস্তফা ইকবাল, জ্যোতির্ময় নন্দী, নাট্যজন মিলন চৌধুরী, শান্তনু বিশ্বাসসহ অনেকেই আড্ডা মৌতাত করে রাখতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।
এই সময়টাতেই ‘অচিরা’ গোষ্ঠী নামে পরিচিত ধীমান ও মননশীল তরুণদের একটি দলের আড্ডা বসত কখনো কবি মোহাম্মদ রফিকের দেবপাহাড়ের বাসভবনে, কখনো কবি আলতাফ হোসেনের পুরনো বিমান অফিস এলাকার বাসভবনে।
প্রকাশ্যে কোনো বিরোধ না থাকলেও সাহিত্যাদর্শের দিক থেকে ‘স্পার্কে’র সঙ্গে ‘অচিরা’র একটা বৈপীরত্য ছিল এটা অনুমান করা সম্ভব। যতদূর মনে পড়ে ওই সময় স্পার্কের একটি পুস্তিকার প্রচ্ছদে শিল্পী হাসি চক্রবর্তীর আঁকা ব্যঙ্গচিত্রে অচিরা গোষ্ঠীর লেখকদের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছিল। তবে এইসব সাহিত্যিক বিরোধ কখনোই মাত্রা ছাড়ায়নি, স্বাভাবিক নিয়মে তা বিলীনও হয়েছে সময়ের স্রোতে।
এই আড্ডায় শামিল হতেন কবি-প্রাবন্ধিক আবুল মোমেন, জিনাত আর রফিক, দিবাকর বড়ুয়া, তপনজ্যোতি বড়ুয়া ও অমিত চন্দ প্রমুখ। এই কবি-লেখকেরা দীর্ঘকাল ‘অচিরা’ নামের একটি ছোট কাগজে তাঁদের সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। পরে আশির দশকের সূচনালগ্নে নন্দনকাননের শিশুদের বহুমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ‘ফুলকিতে’ অচিরা পত্রিকার নামের সঙ্গে মিল রেখে গড়ে ওঠে একটি পাঠচক্র। আবুল মোমেন ছিলেন এই পাঠচক্রের মধ্যমণি। তাঁর বন্ধু কবি ও অনুবাদক তপনজ্যোতি বড়ুয়া এই উদ্যোগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। মূলত আড্ডাই। কিন্তু সপ্তাহে শুধু ছুটির একটি দিনে জমে ওঠা এই আড্ডার বৈশিষ্ট্য ছিল লাগামছাড়া গল্পগুজবের পরিবর্তে এখানে নিজেদের লেখা পড়ে শোনানো, সেই লেখার ওপর অন্যদের মতামত প্রকাশ, ধ্রুপদী সাহিত্য থেকে পাঠ ইত্যাদি। এক ঝাঁক তরুণ লেখকের রুচি ও মনন ঋদ্ধ হয়েছে ‘অচিরা পাঠচক্রে’ এসে। রণজিৎ বিশ্বাস, জ্যোতির্ময় নন্দী, ওমর কায়সার, কাজী সুফিয়া আক্তার, অজয় দাশগুপ্ত, শ্যামল দত্ত, সেলিনা শেলী, দেবাশিস ভট্টাচার্য, ইব্রাহিম আজাদ, উত্তম সেন, সনতোষ বড়ুয়া, নুরুন্নাহার শিরীন, মুনির আহমদ, প্রলয় দেব, দুলাল দাশগুপ্ত ও বর্তমান নিবন্ধকারসহ এক ঝাঁক তরুণ কবিলেখক সংস্কৃতিকর্মী সমবেত হয়েছিলেন এই আড্ডায়। মাঝে মাঝে ঢাকা থেকে অগ্রগণ্য সাংস্কৃতিক সংগঠক ও সঙ্গীতজ্ঞ ওয়াহিদুল হক এবং ফুল্অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সঙ্গীতশিল্পী শীলা মোমেন এসে যোগ দিলে আড্ডা নতুন মাত্রা পেত। নানা সময়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুসন্ধিৎসু গবেষক উইলিয়াম রাঁদিচে, ফ্রান্স ভট্টাচার্য, কথাশিল্পী গৌরিকিশোর ঘোষ, কবি শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, কাব্যসমালোচক অরুণ সেন, নাট্যগবেষক বিষ্ণু বসুসহ দেশ-বিদেশের স্বনামখ্যাত ব্যক্তিবর্গের আগমনে অচিরার আড্ডা প্রাণবন্ত ও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। নব আঙ্গিকে ‘অচিরা’ পত্রিকারও বেশ কিছু সংখ্যা প্রকাশিত হয় তখন।